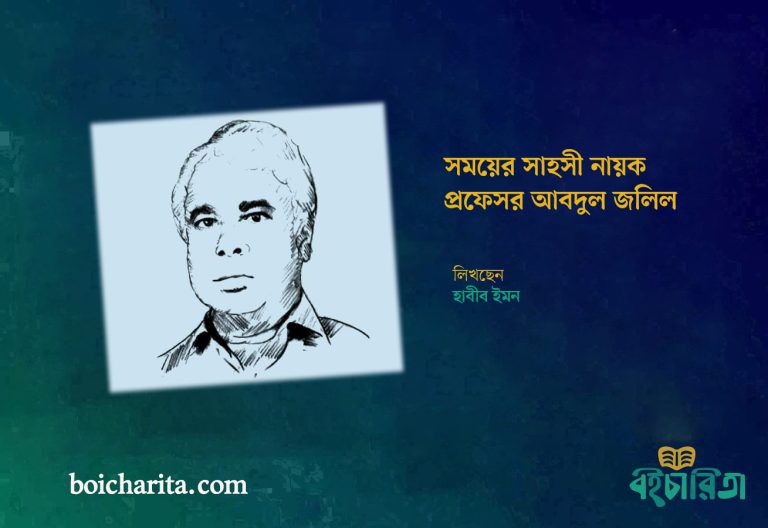কার নির্দেশে খালেদ, হুদা এবং হায়দারকে হত্যা করা হয়েছিল?

এক
কারাগারের ভেতরে অবিসংবাদিত চার নেতাকে হত্যা—ইতিহাসের এমন ঘটনা কমই আছে। তবে একদমই নেই, এ কথা বলা যাচ্ছে না। দেশের ইতিহাসে প্রথম জেলহত্যা রাজশাহীর খাপড়া ওয়ার্ড। ১৯৫০ সালের ২৪ এপ্রিল রাজশাহী কেন্দ্রীয় কারাগারে সংঘটিত গণহত্যায় সাত জন জেলবন্দী ব্যক্তিকে হত্যা করা হয়। তো, ১৯৭৫ সালের ৩ নভেম্বর ভোরে ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারের নির্জন প্রকোষ্ঠে চার জাতীয় নেতা বাংলাদেশের প্রথম সরকারের উপ-রাষ্ট্রপতি সৈয়দ নজরুল ইসলাম, প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দীন আহমদ, অর্থমন্ত্রী ক্যাপ্টেন এম মনসুর আলী এবং স্বরাষ্ট্র, ত্রাণ ও পুনর্বাসন মন্ত্রী এ এইচ এম কামারুজ্জামানকে বন্দী অবস্থায় নৃশংসভাবে হত্যা করা হয়।
দেশমাতৃকার জাতীয় এই চার নেতাকে শুধু গুলি চালিয়েই ক্ষান্ত হয়নি, কাপুরুষের মতো গুলিবিদ্ধ দেহকে বেয়নেট দিয়ে খুঁচিয়ে ক্ষত-বিক্ষত করে জ্বালা মিটিয়েছিল ঘাতকরা। কারাগারের নিরাপদ আশ্রয়ে থাকা অবস্থায় এ ধরনের বর্বরোচিত-নিষ্ঠুর হত্যাকাণ্ড পৃথিবীর ইতিহাসে বিরল।
সাংবাদিক অ্যান্থনি মাসকারেনহাস তার ‘বাংলাদেশ এ লিগ্যাসি অব ব্লাড’ বইয়ে চার নেতার হত্যাকাণ্ডের বিষয়ে বিস্তারিত বর্ণনা দিয়েছেন। আমাদের অবশ্যই স্মরণ করা জরুরি, এই চারজন নেতার নেতৃত্বে ১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধ পরিচালিত হয়। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের অনুপস্থিতিতে মুজিবনগর সরকার গঠন করে মুক্তিযোদ্ধাদের সঠিকপথে পরিচালনা করে বিজয়কে ত্বরান্বিত করেন তারা। মুক্তিযুদ্ধের প্রশ্নের এদের অবদানকে কোনোভাবে খাঁটো করে দেখা সঠিক পন্থা নয়। সেই আলোচনা আমাদের তোলা উচিত।
তবে, এ চার নেতা জেলখানায় হত্যার শিকার হয়ে ইতিহাসে একটু হলেও বেঁচে আছেন। বছরে একদিন হলেও তারা ৩ নভেম্বর আলোচনায় আসেন। আর বাদবাকি দিন?
দুই
শেখ মুজিবকে হত্যার প্রায় আড়াই মাস পরে কারাগারে এ চার নেতাকে কেন হত্যা করা হয়েছিল? বঙ্গবন্ধু হত্যাকাণ্ডের পর আওয়ামী লীগের নেতৃত্ব তখন অনেকটা দিকবিদ্বিকশূন্য। ওই চারজন জ্যেষ্ঠ নেতাসহ অনেকেই কারাগারে, অনেকে আত্মগোপনে ছিলেন। বাকি নেতারা প্রকাশ্য কিংবা অপ্রকাশ্যে খন্দকার মোশতাক আহমেদের সঙ্গে সমঝোতা করেন। অনেকে আবার রাজনীতিতে নিষ্ক্রিয় হয়ে যান। তবে আওয়ামী লীগের রাজনীতি ঘুরে দাঁড়িয়েছে। ইতিহাসের সেই নিরিখে এখন প্রশ্ন হলো, প্রশ্ন হচ্ছে, শেখ হাসিনার পরে আওয়ামী লীগের চার নেতা কে কে? আবদুস সামাদ আজাদ কে? জোহরা তাজউদ্দীন কে? আবদুল মালেক উকিল কে? জিল্লুর রহমান কে? শেখ হাসিনার পরে যেসব দলীয় নেতা আছে এরা কি ইতিহাসে স্থান পাবে?
রাজনৈতিক বিশ্লেষক ও গবেষক মহিউদ্দিন আহমেদ মনে করেন, জেল হত্যাকাণ্ডের সঙ্গে ৩ নভেম্বর খালেদ মোশাররফের নেতৃত্বে পাল্টা সামরিক অভ্যুত্থানের ঘটনার সম্পৃক্ততা রয়েছে। কেননা মুজিব হত্যাকারী সেনা কর্মকর্তারা ভেবেছিলেন খালেদ মোশারফের নেতৃত্বে সে অভ্যুত্থান আওয়ামী লীগের পক্ষে হচ্ছে। কিন্তু খালেদ মোশাররফ এবং তার সমর্থকদের কার্যকলাপ থেকে এ ধরনের কোনো প্রমাণ পাওয়া যায়নি বলে লেখক তা উল্লেখ করেন। বিগ্রেডিয়ার (অব.) এম সাখাওয়াত হোসেনও তার লেখায় তেমনটা উল্লেখ করতে পারেননি।
সেই সময়ের ঘটনাধারা এবং বিভিন্ন ব্যক্তির ভূমিকা নিয়ে যে প্রশ্নসমূহ উঠে আসে কখনো তার উত্তর আলোচিত হয়নি, আবার কখনো তা পাওয়া গিয়েছে বিভিন্নভাবে। ফলে সেই ঘটনাগুলো নিয়ে টিকে থাকছে নানা বিতর্ক, আবার অস্পষ্টতাও দূর হচ্ছে না। প্রয়োজন সেই সময়ের বিভিন্ন দিক নিয়ে নৈর্ব্যক্তিক ও বস্তুনিষ্ঠ বিশ্লেষণ।
এই ঘটনাগুলো ঘটে চললেও এই অভ্যুত্থানের প্রধান ব্যক্তি খালেদ মোশাররফ দেশের মানুষের উদ্দেশ্যে রেডিও-টেলিভিশনের মাধ্যমে কোনো বক্তব্য দেননি। ফলে দেশের মানুষ এবং বিভিন্ন সেনানিবাসের সাধারণ সৈনিকদের কাছে এই অভ্যুত্থানের উদ্দেশ্য সম্পর্কে তৈরি হয় অস্পষ্ট ধারণা। শাফায়াত জামিল এবং অন্য অফিসারদের অনেক অনুরোধ সত্ত্বেও খালেদ মোশাররফ রেডিও-টেলিভিশনে ভাষণ দিতে অনীহা প্রকাশ করেন। তার মত ছিল, কেবল নতুন প্রেসিডেন্টই এই দায়িত্বটি পালন করতে পারেন (জামিল, পৃ-১৩৯)।
এই অভ্যুত্থানের প্রধান ব্যক্তি খালেদ মোশাররফ দেশের মানুষের উদ্দেশ্যে রেডিও-টেলিভিশনের মাধ্যমে কোনো বক্তব্য রাখেননি। ফলে দেশের মানুষ এবং বিভিন্ন সেনানিবাসের সাধারণ সৈনিকদের কাছে এই অভ্যুত্থানের উদ্দেশ্য সম্পর্কে তৈরি হয় অস্পষ্ট ধারণা। শাফায়াত জামিল এবং অন্য অফিসারদের অনেক অনুরোধ সত্ত্বেও খালেদ মোশাররফ রেডিও-টেলিভিশনে ভাষণ দিতে অনীহা প্রকাশ করেন। তার মত ছিল, কেবল নতুন রাষ্ট্রপতিই এই দায়িত্বটি পালন করতে পারেন (জামিল, পৃ-১৩৯)।
খালেদ মোশাররফের এমন আচরণ স্পষ্ট করে যে, সেনা অভ্যুত্থানের মধ্যে দিয়ে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা দখলের অভিপ্রায় খালেদ মোশাররফের ছিল না। কিন্তু যখন একটি সেনা অভ্যুত্থানের নেতৃত্বই তিনি দিয়েছিলেন, তখন সেই অভ্যুত্থানের লক্ষ্য সম্পর্কে দেশের মানুষকে অবহিত করার দায়িত্বটিও তারই ছিল।
দেশের মানুষের সঙ্গে যোগাযোগ না করে তার নিশ্চুপ থাকার পুরো সুযোগটি গ্রহণ করে সেনাবাহিনী এবং সেনাবাহিনীর বাইরের খালেদ-বিরোধীরা। খালেদ মোশাররফ ভারত এবং আওয়ামী লীগের স্বার্থ রক্ষার জন্য অভ্যুত্থান করেছেন এমন বক্তব্য রটিয়ে দেওয়া হয় (সাখাওয়াত হোসেন: ২০০৭, পৃ-১০১, পারভেজ: ১৯৯৫, পৃ-১২১)। যদিও খালেদ মোশাররফের অভ্যুত্থানে সমর্থন যোগানোর কোনো ভারতীয় চেষ্টার কোনো প্রমাণ মহিউদ্দিন আহমেদ বা সাখাওয়াত হোসেন কখনো প্রমাণ করতে পারেননি।
মহিউদ্দিন আহমেদের লেখা থেকে জানা যায়, “ক্ষমতাসীন মোশতাক বা তার সমর্থকরা চাননি যে তাদের বিরোধী আরেকটি শক্তি শাসন ক্ষমতায় পুনর্বহাল হোক। ওই ধরনের একটা সরকার যদি হতো তাহলে জেলে থাকা সে চারজন ছিলেন সম্ভাব্য নেতা।” তার ধারণা, এ সম্ভাবনা থেকে জেল হত্যাকাণ্ড হতে পারে।
পর্যবেক্ষকদের দৃষ্টিতে শেখ মুজিবুর রহমানকে হত্যার পর থেকেই হত্যাকারী সেনা কর্মকর্তারা পাল্টা আরেকটি অভ্যুত্থানের আশংকায় ছিল। সেনাবাহিনীর মধ্যে ছিল এক ধরনের বিশৃঙ্খলা। জ্যেষ্ঠ সেনা কর্মকর্তাদের মধ্যে ছিল ক্ষমতার দ্বন্দ্ব। একদিকে মেজর জেনারেল জিয়াউর রহমান এবং অন্যদিকে মেজর জেনারেল খালেদ মোশারফ।
তখন ঢাকা সেনানিবাসে মেজর পদমর্যাদায় কর্মরত ছিলেন বিগ্রেডিয়ার (অব.) এম সাখাওয়াত হোসেন। তিনি এসব ঘটনা প্রবাহ বেশ কাছ থেকে দেখেছেন। তাঁর সে অভিজ্ঞতা নিয়ে সাখাওয়াত হোসেন একটি বই লিখেছেন—‘বাংলাদেশ রক্তাক্ত অধ্যায়: ১৯৭৫-৮১’।
সাখাওয়াত হোসেন বলেন, বঙ্গভবনের থাকা সেনা কর্মকর্তাদের সঙ্গে একটা সংঘাত চলছিল সেনানিবাসের উর্ধ্বতন কিছু সেনা কর্মকর্তাদের সঙ্গে। সাখাওয়াত হোসেন বলেন, “খন্দকার মোশতাক যে বেশিদিন ওখানে টিকবেন না, এটাও ক্যান্টনমেন্টের ভেতরে সিনিয়র অফিসারদের মধ্যে একটা ধারণা জন্মেছিল। তখন আবার সিনিয়র অফিসারদের মধ্যেও ক্ষমতার দ্বন্দ্ব ছিল।”
শেখ মুজিবকে হত্যাকারী সেনা কর্মকর্তারা ধারণা করেছিলেন যে কোনো পাল্টা অভ্যুত্থান হলে সেটি আওয়ামী লীগের সমর্থন পাবে। সে ধরনের পরিস্থিতি হলে কী করতে হবে সে বিষয়ে মুজিব হত্যাকারী সেনা কর্মকর্তারা কিছুটা ভেবেও রেখেছিলেন।
সাখাওয়াত হোসেন বলেন, “ঐ ধরনের ক্যু হলে তখনকার আওয়ামী লীগে যাতে কোনো্ ধরনের লিডারশিপ না থাকে সেটাই তারা বোধ হয় নিশ্চিত করেছিল।” হত্যাকারী সেনা কর্মকর্তারা ভেবেছিল যদি সে চারজন রাজনীতিবিদকে যদি হত্যা করা হয় তাহলে পাল্টা অভ্যুত্থান হলেও সেটি রাজনৈতিক সমর্থন পাবে না।
তিন
১৫ আগস্ট সামরিক বাহিনী ক্ষমতার বারান্দায় ঢুকে পড়েছিল। ৩ নভেম্বরের পর তারা ঢুকল একেবারে রাজমহলে। তবে ৩ নভেম্বরের অভ্যুত্থানকারীরা সরকারের ‘সিভিলিয়ান’ মুখোশটা আর রাখলেন না। জারি হলো পুরোপুরি সেনাশাসন। ৩ নভেম্বর অভ্যুত্থানের প্রধান দিক দুটি। এই অভ্যুত্থানের কারণে মোশতাক সরকারের পতনের মধ্য দিয়ে পুরোদস্তুর সামরিক শাসন শুরু হয়। দ্বিতীয়ত, এই ডামাডোলে জেলে আটক চার নেতা নিহত হন। এটা এখন মোটামুটি স্পষ্ট যে খালেদের অভ্যুত্থানের পেছনে কোনো রাজনৈতিক সরকার প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্য ছিল না। তাদের পরিকল্পনায় চার নেতা ছিলেন না। যদি থাকতেন, তাহলে শুরুতেই খালেদ ও তার সঙ্গীরা চার নেতাকে মুক্ত করতে জেলখানায় ছুটে যেতেন। তারা সেটা করেননি। তারা ৩ তারিখ সারা দিন ওই নেতাদের খোঁজও নেননি।
চার
ছাত্র-জনতার গণ-অভ্যুত্থানের পর অনেকে জাতীয় চার নেতাকে ইতিহাসে পুনঃস্থাপনের কথা বলেছেন। বঙ্গবন্ধুর প্রতিদ্বন্ধী নেতা হিসেবে তাঁদেরকে সামনে নিয়ে আসার কথা বলেছেন কেউ কেউ। এ মিমাংসাটা করা হয়নি—বঙ্গবন্ধুর মর্যাদা কোথায় থাকা উচিত, জাতীয় চার নেতাদের আমরা কোন স্থানে রাখব?
আমরা বলছি, বঙ্গবন্ধুর পাশাপাশি ইতিহাসের অপরাপর চরিত্রগুলোকে মূল্যায়ন ও মর্যাদা দেওয়া উচিত। তবে তাতে ফারাক আছে। আমাদের ভাষ্যে রাজনৈতিক সততা আছে, তাদের মধ্যে সেটি নেই। বরং আরেকটি ফ্যাসিবাদ বয়ান তৈরির অভিপ্রায় আছে। কিন্তু ইতিহাসের এই চার নেতার অবদানকে আমরা কিভাবে মূল্যায়ন করছি, যেভাবে তাদেরকে হত্যা করা হয়েছে,তাদেরকে আমরা কিভাবে স্মরণ করছি,প্রশ্নটা হলো সেখানে। কেবলমাত্র ইতিহাসের পাল্টা বয়ান দিতে ফ্যাসিবাদী বয়ানকেই সংহত করছি না তো,উসকেও দিচ্ছি। এই প্রশ্নটাও নির্মোহভাবে তোলা দরকার, ৭ নভেম্বর সকালে একদল সৈন্য জেনারেল খালেদ আর তার সঙ্গের দুই বীর মুক্তিযোদ্ধা অফিসারকে গুলি করে হত্যা করে। এই হত্যাকাণ্ডে ১০ বেঙ্গলের দুজন অফিসার মেজর জলিল আর মেজর আসাদও অংশ নেয় (সাখাওয়াত হোসেন, পৃ-১১১)। কার নির্দেশে খালেদ, হুদা এবং হায়দারকে হত্যা করা হয়েছিল?
হাবীব ইমন : রাজনৈতিক বিশ্লেষক