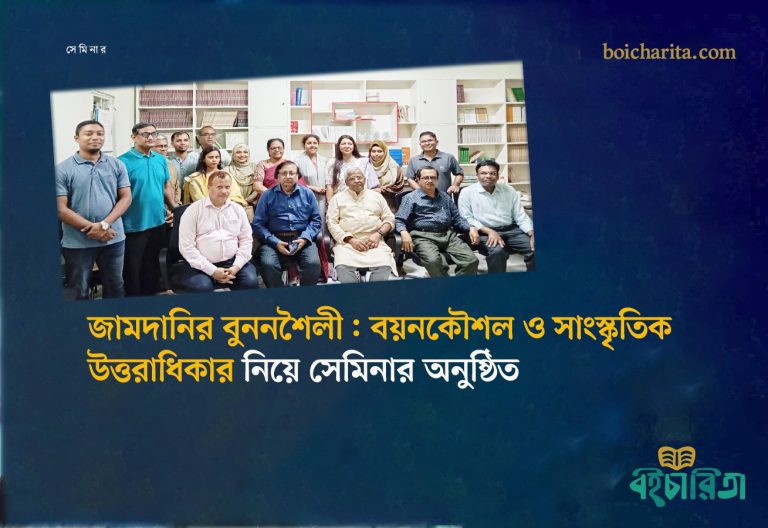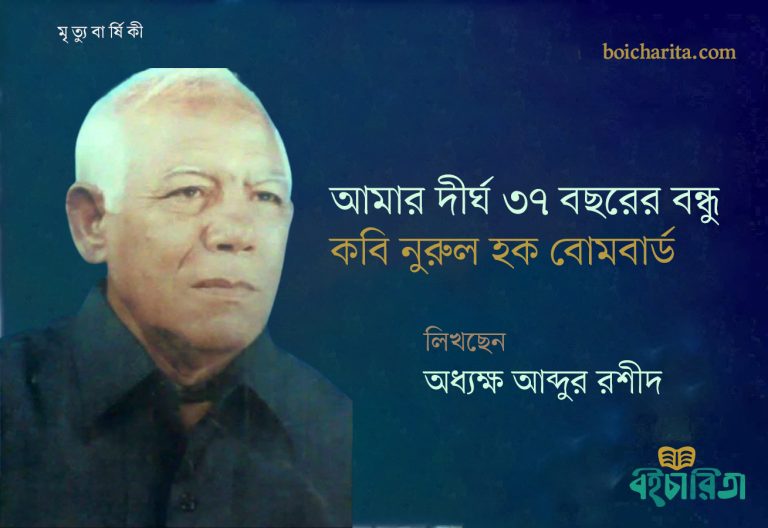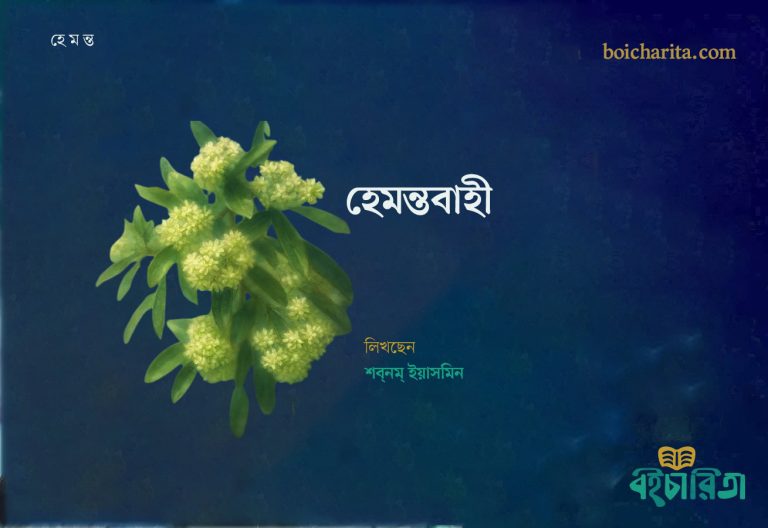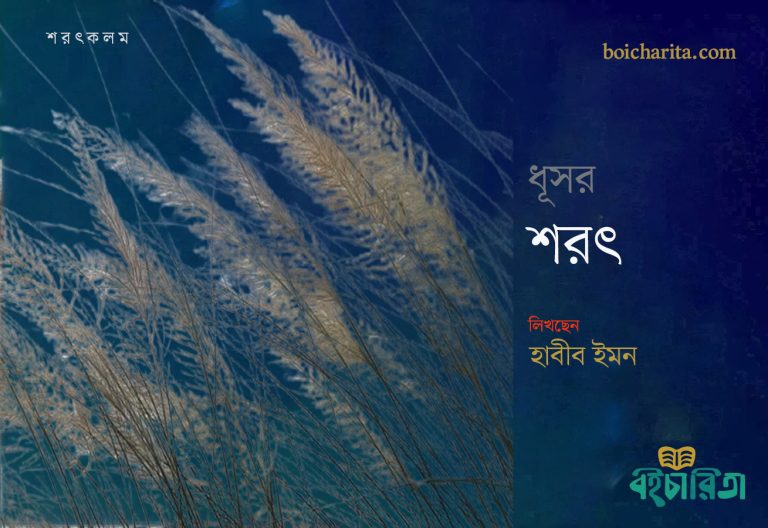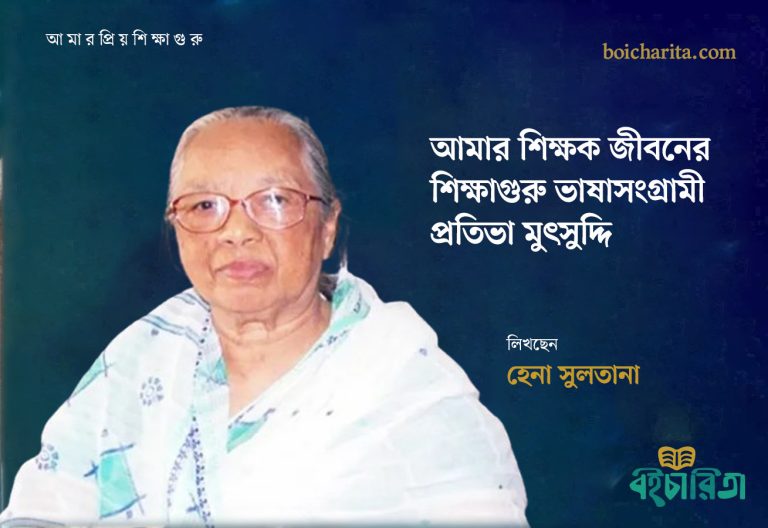রবীন্দ্রনাথ-নজরুল-সুকান্ত : বাংলা চেতনার ত্রিকোণ

বাংলা সাহিত্যে তিনটি পরিপূরক পাল—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮৬১-১৯৪১), কাজী নজরুল ইসলাম (১৮৯৯-১৯৭৬) এবং সুকান্ত ভট্টাচার্য (১৯২৬-১৯৪৭)। তারা যথাক্রমে মহত্ত, বিদ্রোহ ও বিপ্লবের প্রতীক হিসেবে প্রতিষ্ঠিত। এই তিন কবি শুধু সময়ের প্রতিনিধিই নন, বরং তারা হয়ে উঠেছেন বাংলার চেতনার ভিন্ন ভিন্ন স্তম্ভ। তবে রাষ্ট্রীয়ভাবে এই তিন কবির চর্চা এবং তাদের স্মরণ আজ সমানভাবে ঘটে না। একসময় জাতীয় ও স্থানীয়ভাবে তাদের জন্মজয়ন্তী পালিত হতো, আজ তা আর হয় না। বিশেষ করে সুকান্তকে প্রায় পুরোপুরি বিস্মরণ করা রাখা হয়েছে। এমনকি নজরুল ও রবীন্দ্রনাথকেও নতুন ধরণের ‘অন্তঃসারশূন্য উৎসবে’ সীমাবদ্ধ রাখা হয়েছে। এই সংকোচনের পেছনে আছে রাজনৈতিক-সাংস্কৃতিক সংকীর্ণতা এবং একটি ক্রমশ হ্রাসমান রাষ্ট্রীয় আদর্শবোধ।
এটা আমরা মানি, না মানি; রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও কাজী নজরুল ইসলাম বাংলা সাহিত্যে দুই মহাপ্রাণ। রবীন্দ্রনাথ ছিলেন মানবতাবাদের, সৃষ্টির অন্তর্নিহিত সংগীতের আর সর্বজনীন চেতনার কবি। আর নজরুল বিদ্রোহের, সাম্যবাদের, নিপীড়িত মানুষের পক্ষে অস্ত্র হাতে তুলে নেওয়া সাহসের কবি। রবীন্দ্রনাথের লেখা ছিল ঐশ্বরিক এবং মানবিক আদর্শের সন্ধানী, যেখানে তিনি বিশ্বমানবতার প্রতি তার দায়বদ্ধতা দেখাতেন। অন্যদিকে, নজরুল ছিলেন ঐতিহাসিক বস্তুবাদের অনুসারী এবং শ্রেণি সংগ্রামকে অগ্রাধিকার দিয়ে তার সাহিত্য রচনা করেছেন। প্রশ্ন থাকতে পারে, নজরুল কী শেষ পর্যন্ত বস্তুবাদের অনুসারী থাকতে পেরেছেন? এর সহজ জবাব, পারেননি। কেন পারেননি, সেই আলাপ ভিন্ন। তবে, নজরুলের কবিতা ও গানগুলো বিপ্লবের দিকে উদ্বুদ্ধ ছিল এবং তার সাহিত্যে শ্রমজীবী মানুষের মুক্তির ডাক ছিল স্পষ্ট। তবে তাদের পার্থক্য সত্ত্বেও, তারা একে অপরকে গভীর শ্রদ্ধা করতেন, তারা কোনোদিন পরস্পরের বিরোধী মেরুতে ছিলেন না। বরং, তাদের মাঝে ছিল এমন এক আত্মিক, গভীর সম্পর্ক—যা রাজনীতি বা শৈল্পিক মতপার্থক্যের ঊর্ধ্বে উঠে এক প্রজন্মের কবিকে আরেক প্রজন্মের কবির প্রতি শ্রদ্ধাশীল করেছে।
১৯২১ সালে নজরুল প্রথম কবি হিসেবে পরিচিত হন তার বিদ্রোহী ধারা ও সাম্যবাদী চেতনার জন্য। ‘বিদ্রোহী’ কবিতাটি প্রকাশের মাধ্যমে বাংলা সাহিত্য এক নতুন কণ্ঠস্বর লাভ করে। সে সময় রবীন্দ্রনাথ ছিলেন তার কাব্যজীবনের মধ্যগগনে। অনেকেই তখন সন্দেহ করেছিল যে রবীন্দ্রনাথ নজরুলের কণ্ঠস্বরকে গ্রহণ করবেন না, বা নতুন এই কবিকে প্রশ্রয় দেবেন না। কিন্তু সে ধারণা ভুল প্রমাণিত হয়।
১৯২২ সালের ডিসেম্বর মাসে যখন নজরুল ‘ধুমকেতু’ নামে একটি সাপ্তাহিক পত্রিকা প্রকাশ শুরু করেন এবং সেখানে ব্রিটিশবিরোধী আগুনঝরানো সম্পাদকীয় লিখে কারাবরণ করেন, তখন রবীন্দ্রনাথ তার প্রতি প্রকাশ্যে সহানুভূতি প্রকাশ করেন। এমনকি নজরুলের বন্দিজীবনের সময়ে রবীন্দ্রনাথ তাকে কবিতা লেখার অনুরোধ করে একটি চিঠিও পাঠান।
সেই চিঠিতে রবীন্দ্রনাথ নজরুলকে লেখেন (তারিখ: ২৬ জানুয়ারি ১৯২৩)—‘নজরুল, তোমার ‘বিদ্রোহী’ কবিতা আমি পড়েছি। এমন তেজ, এমন আগুন আমার পড়া অন্য কোনো কবিতায় পাইনি। তোমার কলম যেন থেমে না যায়। তুমি লেখো। তোমার প্রয়োজন আমাদের সবারই।’ এই চিঠি নজরুলের জীবনে যুগান্তকারী মুহূর্ত। কারাবন্দি অবস্থায় এই চিঠি পেয়ে তিনি চোখে পানি এনে লিখেছিলেন—‘রবীন্দ্রনাথের আশীর্বাদ পেয়েই আমি আজ নজরুল। ওঁর চিঠি আমার কাছে নবজন্মের মতো।’
এ ছাড়া নজরুল যখন জেলে অনশন করছিলেন ৩৯ দিন ধরে, তখন রবীন্দ্রনাথ গভীর উদ্বেগে আক্রান্ত। তিনি পত্র লিখে নজরুলকে অনশন ত্যাগের অনুরোধ করেন। নজরুল সে অনুরোধ রেখেই অনশন ভেঙেছিলেন। এই ঘটনার সংবাদ পরদিন কলকাতার ‘বসুমতী’ ও ‘দৈনিক বঙ্গীয়’ পত্রিকায় প্রধান সংবাদ হয়ে প্রকাশিত হয়।
এই ঘটনাগুলো বাংলা সাহিত্যজগতের ইতিহাসে এক বিরল কিংবদন্তী দৃষ্টান্ত হয়ে রয়ে গেছে—যেখানে এক কবির রাজনৈতিক বিপ্লব, অন্য কবির নন্দনতাত্ত্বিক দর্শনের সঙ্গে দ্বন্দ্বে না গিয়ে সংবেদনশীলতার দার্শনিক মিল তৈরি করে।
রবীন্দ্রনাথ নজরুলের কবিতা উৎসর্গ করে তার ‘বসন্ত’ নাটকটি ১৯২৮ সালে প্রকাশ করেন। উৎসর্গপত্রে তিনি লেখেন—‘এই ক্ষণজন্মা প্রতিভার মাঝে আমি বাংলাদেশের নবযৌবনের ভাষা শুনেছি। বিদ্রোহ, প্রেম আর করুণার স্বর তার কবিতায় একাকার হয়ে ধ্বনিত হয়। আমি তাকে আশীর্বাদ করি।’

অপরদিকে নজরুল রবীন্দ্রাথের মৃত্যুতে গভীর শোকে লিখেছিলেন সেই বিখ্যাত কবিতা:
‘ঘুমাইতে দাও শ্রান্ত কবিরে জাগায়ো না, জাগায়ো না—
সারাজীবন যে আলো দিল ডেকে তার ঘুম ভাঙায়ো না।’
কবিতাটি আকাশবাণীতে আবৃত্তি করতে গিয়ে তিনি এতটাই আবেগে আক্রান্ত হন যে, তার জিহ্বা আড়ষ্ট হয়ে যায়, উচ্চারণ থেমে যায়, এবং চিকিৎসাবিজ্ঞানীরা পরে বলেন—ওই মুহূর্তেই নজরুলের মস্তিষ্কে প্রথম পক্ষাঘাতের লক্ষণ দেখা দেয়। অনেকের মতে, সেই ক্ষণটি নজরুলের কাব্যিক জীবনের সমাপ্তি নির্দেশ করেছিল। এ ঘটনা প্রায় প্রতীকমূলক—যেন বাংলা কবিতার একটি যুগের সমাপ্তির সঙ্গে সঙ্গেই আরেকটি মুখ স্তব্ধ হয়ে গেল।
এমন ঘটনা একমাত্র তখনই সম্ভব, যখন একটি সৃজনশীল সম্পর্ক শুধু পারস্পরিক শ্রদ্ধায় নয়, হৃদয়ের গভীর সংযোগে নির্মিত হয়। রবীন্দ্রনাথ ও নজরুল—দু’জনেই একে অপরের মহত্ত্বকে স্বীকার করেছেন, এবং সমকালীন কিংবা পরবর্তী রাজনৈতিক বিভাজন সেই আন্তরিকতাকে ছিন্ন করতে পারেনি। তবে, নজরুলের আকস্মিক অসুস্থতা, বাকশক্তির পেছনে নানা কল্পগল্প তৈরি করা হয়েছে, যেখানে রবীন্দ্রনাথকে নজরুলের প্রতিপক্ষ হিসেবে দাঁড় করানোর প্রয়াস নেওয়া হয়েছে। যেটা এখনও বিদ্যমান।
১৯৪১ সালে সুকান্ত কলকাতা রেডিওর গল্পদাদুর আসরে যোগদান করেন। সেখানে প্রথমে তিনি রবীন্দ্রনাথের কবিতা আবৃত্তি করেন। রবীন্দ্রনাথের মৃত্যু পর সেই আসরেই নিজের লেখা কবিতা পাঠ করে তাকে শ্রদ্ধা জানান।
রবীন্দ্রনাথের দার্শনিক মননে হেগেলিয় চেতনার ছায়া দেখা যায়—বিশ্বসত্তা, একক আত্মার সঙ্গে ঐশ্বরিক মিলন, একটি সর্বজনীন মানবতাবোধ। তবে রাশিয়া সফর রবীন্দ্রনাথের মনস্ত¡াত্ত্বিক জায়গাটা কিছুটা নাড়া দেয়, যেটা তার শনিবারের চিঠি-তে পাওয়া যায়। অন্যদিকে, নজরুলের দৃষ্টিভঙ্গিতে মার্কসীয় শ্রেণিসংগ্রাম, বস্তুনিষ্ঠ ইতিহাসবোধ ও চেতনার পরিবর্তনশীলতা বেশি প্রবল। মার্কস যেমন পত্রিকা সম্পাদনা করে রাষ্ট্রের রোষানলে পড়েছিলেন, নজরুলও ‘ধুমকেতু’ সম্পাদনা করে একই অভিজ্ঞতার ভেতর দিয়ে গেছেন। তারা দু’জনেই দারিদ্র্য বরণ করেছিলেন বিপ্লবী আদর্শের কারণে। এই মিল নিছক রাজনৈতিক নয়, এটা ছিল অস্তিত্ববাদী।
রবীন্দ্রনাথ, তার দীর্ঘ সৃষ্টিশীল জীবনে, বাংলা সাহিত্যকে এক নতুন দিগন্তে নিয়ে গেছেন এবং বিশ্বসাহিত্যে গীতিকবিতার ক্ষেত্রে এক অপ্রতিদ্বন্দ্বী স্থানে দাঁড়িয়ে আছেন। অন্যদিকে, নজরুল ইসলাম, যার সৃষ্টিশীল জীবন ছিল মাত্র ২২ বছরের, রবীন্দ্রনাথের তুলনায় সময়ের হিসেবেও ছোট ছিল। তবে এই সীমিত সময়েও নজরুল বাংলা কবিতার ইতিহাসে এক অসামান্য প্রতিভা হিসেবে স্বীকৃত। তিনি শুধুমাত্র গীতিকার নন, সমাজের আন্দোলন ও বিপ্লবের পক্ষে তার সৃষ্টির মাধ্যমে একটি শক্তিশালী বার্তা দিয়েছিলেন।
আবার, সুকান্ত ভট্টাচার্য ছিলেন নজরুলের বিপ্লবী কাব্যচেতনার প্রত্যক্ষ উত্তরাধিকার। যেন নজরুলের এক তরুণ আত্মা—তবে তিনি নজরুলের চেয়ে আরও স্পষ্ট মার্কসীয় রাজনীতিতে দাঁড়িয়ে ছিলেন। নজরুলের মতো, সুকান্তও তার কবিতায় শ্রমজীবী মানুষের অভাব, যুদ্ধ, পুঁজিবাদ বিরোধিতা, বিপ্লব এবং একটি শ্রেণিহীন সমাজের স্বপ্ন স্পষ্ট হয়ে ওঠে।
সুকান্ত লিখেছিলেন—
‘চলে যাব—তবু আজ যতক্ষণ দেহে আছে প্রাণ
প্রাণপণে পৃথিবীর সরাব জঞ্জাল,
এ আমার শপথ।’
এই ‘জঞ্জাল’ সরানোর শপথই তাকে নজরুলের বিপ্লবী উত্তরাধিকার হিসেবে স্থাপন করে। নজরুলের বিপ্লব অনেক সময় রোমান্টিক ছন্দে উচ্চারিত হয়েছে। কিন্তু সুকান্তের কণ্ঠ ছিল কঠিন, বাস্তববাদী, শ্রেণিবাদী এবং বিপ্লব-সংগঠনের জন্য নিবেদিত। তার সাহিত্যকর্ম যেমন ‘ছাড়পত্র’, ‘ঘুম নেই’, কিংবা ‘হে মহাজীবন’ কেবল কবিতা নয়—সেগুলো ছিল রাজনৈতিক স্লোগান, তীব্র এক দার্শনিক চেতনার সাক্ষ্য। তার লেখায় ‘মুক্তির সংগ্রাম’ স্পষ্ট ছিল, এবং তার কবিতায় মার্কসবাদী চেতনা ও বিপ্লবী মনোভাব প্রতিফলিত হয়েছে। ‘ক্ষুধার রাজ্যে পৃথিবী গদ্যময়’—এই পঙতিটি শুধু কাব্যিক নয়, এটি একটি রাজনৈতিক ভাষ্যও বটে। তার কবিতায় শ্রমিক, কৃষক, বঞ্চিত মানুষ, নারীর শ্রম—সব কিছুই এসেছে শ্রেণিসংগ্রামের বাস্তবতা থেকে।
১৯৪৭ সালে তার মৃত্যু হয় মাত্র ২১ বছর বয়সে। কিন্তু এই অল্প বয়সেই তিনি নির্মাণ করেছিলেন এক ভিন্ন ধরণের কবিতা—যা কল্পনার চেয়ে বাস্তবকে বেশি গুরুত্ব দেয়, যা শৃঙ্খলিত উপমার চেয়ে নির্ভেজাল আর্তনাদে বেশি বিশ্বাস করে। রবীন্দ্র-নজরুল যেমন কেবল মাত্র কবি ছিলেন না, সাহিত্যের সকল ক্ষেত্রে তার ছিল অবাধ বিচরণ। তেমনি সুকান্তও ওই বয়সেই কবিতা ছাড়াও লিখেছিলেন গান, গল্প, নাটক এবং প্রবন্ধ। তার ‘ছন্দ ও আবৃত্তি’ প্রবন্ধটি পাঠে বেশ বোঝা যায় ওই বয়সেই তিনি বাংলা ছন্দের প্রায়োগিক দিকটিই শুধু আয়ত্বে আনেননি, সে নিয়ে ভালো তাত্ত্বিক দক্ষতাও অর্জন করেছিলেন। বিপ্লবী রোমান্টিসিজম বা প্রথাগত কমিউনিজমের আদতে নয়, প্রকৃতঅর্থে কমিউনিজম ছিল সুকান্তের প্রেরণা, ধ্যান-জ্ঞান। যা আজও আমাদের আন্দোলন-সংগ্রামের ভাষা জোগায়। সুকান্ত যেন বাংলা কাব্যভাষায় সর্বহারা শ্রেণির চেতনার একটি অগ্নিস্ফুলিঙ্গ হয়ে উঠেছিলেন।
এই প্রত্যক্ষ রাজনীতিকরণ তাকে রাষ্ট্র ও শাসকশ্রেণির কাছে গ্রহণযোগ্য করে তোলে না, বরং বামপন্থী রাজনীতির অংশ হিসেবে তাকে পাঠ করা হয়। তাঁর কণ্ঠস্বর ছিল তরুণ, স্পষ্ট, প্রতিবাদী, এবং একেবারেই রাষ্ট্রবিরোধী স্বরকে ধারণকারী। ফলে বাংলাদেশে রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে তার জন্মজয়ন্তী কিংবা মৃত্যুবার্ষিকী যথাযথ মর্যাদায় পালন করা হয় না, যদিও তিনি বাংলাদেশের কবিদেরও কবি। তার পৈত্রিক নিবাস ছিল ফরিদপুর জেলার [বর্তমান গোপালগঞ্জ জেলার কোটালীপাড়া থানার উনশিয়া গ্রামে]। সুকান্তকে অনেকে রবীন্দ্র-নজরুলের যুগল উত্তরসূরি মনে করেন—তিনি রবীন্দ্র-আবেগের ছায়া যেমন বহন করেছেন, তেমনি নজরুল-প্রতিবাদের ভাষাও আত্মস্থ করেছেন। কিন্তু এখানেই তাকে থামিয়ে দিলে ভুল হবে। সুকান্ত উত্তরাধিকার বহনকারীই শুধু নন—তিনি ছিলেন একটি ভাঙনের যুগে জন্ম নেওয়া এক নবযুগের কণ্ঠস্বর।
এটি অত্যন্ত দুঃখজনক যে, স্বাধীনতা পরবর্তী বাংলাদেশে সুকান্ত ভট্টাচার্যকে রাষ্ট্রীয়ভাবে উপেক্ষা করা হয়েছে। তার জন্ম ও মৃত্যুদিনে একসময় রাষ্ট্রীয় অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হলেও, বর্তমানে তা একপ্রকার বন্ধ হয়ে গেছে। যদিও সুকান্তের সাহিত্য কেবল কাব্যিক চেতনাতেই নয়, তার সামাজিক ও রাজনৈতিক প্রভাবেও অতুলনীয়, তারপরও তাকে যথাযথ সম্মান দেওয়া হয়নি। তার রাজনৈতিক সংগ্রামী সত্তা এবং শ্রমিক শ্রেণির প্রতি সহানুভূতির কারণে তাকে ‘মার্কসবাদী’ কবি হিসেবে উপস্থাপন করা হয়ে থাকে, যার প্রভাব রাজনৈতিক ক্ষেত্রে নেতিবাচক হতে পারে।
১৯৭০ ও ৮০-র দশকে স্কুল-কলেজে বা রাষ্ট্রীয় ও স্থানীয় পর্যায়ে এই তিন কবির জন্মজয়ন্তী উদযাপন হতো। অতীতে দেখা যেত—পহেলা বৈশাখের আগে-পিছে রবীন্দ্র জন্মজয়ন্তী, মে মাসে নজরুল জন্মজয়ন্তী, আবার সুকান্তের জন্ম ও মৃত্যু উপলক্ষে বামপন্থী সাংস্কৃতিক সংগঠনগুলোর নানা আয়োজন। কিন্তু ধীরে ধীরে এই তিন কবির উৎসব রাষ্ট্রের প্রাতিষ্ঠানিক আয়োজনে স্থান হারিয়েছে।
বর্তমান বাংলাদেশে রবীন্দ্রনাথ ও নজরুলের স্মরণ সীমিত কিছু অনুষ্ঠানের মধ্যে সীমাবদ্ধ—কখনো তা সরকারি দায়সারা আয়োজন, কখনো তা দলীয় ‘সংস্কৃতি কর্মসূচি’। এবার দেখা গেল, রাষ্ট্রীয়ভাবে রবীন্দ্রনাথ প্রায় উপেক্ষিত। নজরুলকে প্রায়শ ব্যবহার করা হয় মুসলিম জাতীয়তাবাদের সাংস্কৃতিক মুখপাত্র হিসেবে; অন্যদিকে রবী›ন্দ্রনাথকে অনেকেই এখনো অযথা ‘হিন্দু সাহিত্যের প্রতিনিধি’ বলে আখ্যায়িত করেন। এই সংকীর্ণ মানসিকতা তাদের বহুস্বরিক সাহিত্যকে সংকুচিত করে দেয়।
আর সুকান্ত? তিনি যেন একপ্রকার গুম হয়েছেন। রাষ্ট্রীয় কোনো অনুষ্ঠানেই তাকে আর স্মরণ করা হয় না। বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ের সাহিত্য পাঠ্যক্রমে সুকান্ত প্রায় অনুপস্থিত। অথচ স্বাধীন বাংলাদেশের জন্ম ও সমাজতান্ত্রিক স্বপ্ন নির্মাণে সুকান্তের কবিতা ছিল অনুপ্রেরণা। প্রশ্ন উঠতে পারে—তাকে উপেক্ষার পেছনে কি তার স্পষ্ট সমাজতান্ত্রিক অবস্থান দায়ী?
আজকের রাষ্ট্রীয় আয়োজন ও পাঠ্যসূচির দিকে তাকালে আমরা দেখতে পাই, এই তিন মহৎ কবির চেতনার বিস্তার খুবই অসমভাবে প্রতিনিধিত্ব পায়। রবীন্দ্রনাথকে কখনও অতিরিক্ত শ্রেণিনিরপেক্ষ করে তুলে ধরা হয়—তার রাজনৈতিক মতাদর্শ ও উপনিবেশবিরোধী অবস্থান প্রায় অদৃশ্য। নজরুলকে শুধুই ‘জাতীয় কবি’ নাম দিয়ে তার সমাজতান্ত্রিক, ধর্মনিরপেক্ষ এবং শ্রেণিবাদী কণ্ঠস্বরকে নির্বিষ করে উপস্থাপন করা হয়। আর সুকান্তকে প্রায় বিস্মৃত করা হয়েছে—একটি মাত্র ‘ক্ষুধার রাজ্যে’ উদ্ধৃত করেই পাঠ শেষ।
এই পেছনে রয়েছে একটি বড় রাজনৈতিক বিভাজন—যেখানে সাহিত্যকে এক সাংস্কৃতিক বুদবুদের মধ্যে সীমাবদ্ধ রেখে তার বিদ্রোহী চরিত্রকে অকার্যকর করে ফেলা হয়। স্বাধীনতা-উত্তর বাংলাদেশে রবীন্দ্রনাথের চর্চা চললেও তাকে রাষ্ট্রীয় নান্দনিকতার ছাঁচে ফেলে ‘অসাম্প্রদায়িকতা’র একমাত্র মুখ করে তোলা হয়েছে, যেন অন্য কেউ এই বোধের ধারক নয়। নজরুলের সাম্যবাদকে চাপা দিয়ে কেবল তার ইসলামিক গান বা জাতীয়তাবাদী চেতনা তুলে ধরা হয়। আর সুকান্ত তো পাঠ্যপুস্তকে একজন ‘অকালপ্রয়াত তরুণ কবি’ হিসেবেই বর্ণিত—তার সমাজতান্ত্রিক বোধকে ছেঁটে ফেলা হয়।
এই প্রবণতা বিপজ্জনক। এই প্রবণতা কেবল সাংস্কৃতিক অবক্ষয় নয়, বরং একটি বৃহৎ রাজনৈতিক প্রক্রিয়ার অংশ—যা ইতিহাস, চেতনা ও সাহিত্যের প্রগতিশীল ধারাকে নিঃশেষ করতে চায়। রাষ্ট্রীয়ভাবে যখন ধর্মীয় জাতিবাদ ব্যবহৃত হয় ক্ষমতার স্বার্থে, তখন প্রগতিশীল মানবিক কণ্ঠস্বর রাষ্ট্রের কাছে অস্বস্তিকর হয়ে ওঠে। রবীন্দ্র-নজরুল ও সুকান্তকে চিরতরে শেষ করে প্রবণতা মানেই তো বাঙালি বহুমাত্রিক সংস্কৃতিকে উপেক্ষামাত্রই। যে সংস্কৃতির সঙ্গে রাজনীতি ও মানবিকবোধ সরাসরি কখনো কখনো জড়িত। বাংলা কবিতার স্তম্ভ—রবীন্দ্রনাথ, নজরুল ও সুকান্ত—যতটা না সময়ের, তার চেয়েও বেশি চেতনার প্রতিনিধিত্ব করেন। একটিকে আলাদা করে অন্যকে খর্ব করা মানেই সাহিত্য ও ইতিহাস উভয়ের সঙ্গে প্রতারণা।
তাদের মাঝে পার্থক্য আছে—অবশ্যই আছে। কিন্তু এই পার্থক্য সাংঘর্ষিক নয়, পরিপূরক। রবীন্দ্রনাথ মানবতার অবিনাশী সৌন্দর্য আবিষ্কারে ব্রতী, নজরুল সেই মানবতার বিপরীতে দাঁড়ানো শোষকের বিরুদ্ধে বিদ্রোহী, আর সুকান্ত সেই বিদ্রোহকে কার্যকর রাজনৈতিক সংগ্রামে রূপ দিতে চেয়েছেন। তারা তিনজন মিলে বাংলা সাহিত্যের নৈতিক, দার্শনিক ও বিপ্লবী ভিত্তিকে নির্মাণ করেছেন। তাদের মধ্যে তুলনা নয়, বরং পারস্পরিক বিচিত্রতা ও যুগপৎ উপস্থিতিই বাংলা সাহিত্যের শক্তি। কিন্তু আজকের রাষ্ট্রীয় নীতিমালায় তারা ভিন্ন ভিন্ন শিবিরে ঠেলে দেওয়া হচ্ছেন—ধর্ম, জাতীয়তাবাদ, কিংবা নিরীহ ‘ঐতিহ্য’ নামের পর্দায় ঢেকে ফেলা হচ্ছে তাদের বিপ্লবী, মানবিক, ও দার্শনিক দৃষ্টিভঙ্গি।
বাংলাদেশ রাষ্ট্র যদি সত্যিকার অর্থে মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় দাঁড়াতে চায়, তবে এদের সবার চিন্তা—বিশ্বমানবতার ঐক্য (রবীন্দ্রনাথ), বিদ্রোহী মানবিকতা (নজরুল), এবং শ্রেণিসচেতন বিপ্লব (সুকান্ত)—এই ত্রিবেণী ধারাকে একত্রে ধারণ করতে হবে। তা না হলে, প্রতিস্পর্ধার বারুদের গন্ধ আরও গাঢ় হবে, আর আমরা শুধু কবিদের জন্মতারিখ মনে রেখে তাদেও প্রতিকৃতির সামনে রেখে ঘরোয়া আয়োজনে মোমবাতি জ্বেলে যাবো—যেমনটি আমরা এখন করি।
আমরা যদি সত্যিই এই তিন কবিকে স্মরণ করতে চাই—তাহলে তা হবে নতুন করে পাঠ করার মধ্য দিয়ে, তাদের পূর্ণ আদর্শ ও মতবাদকে বোঝার চেষ্টা করে। শুধু জন্মদিন পালনের মধ্যে নয়, বরং তাদের কবিতার শ্লোককে রাজনৈতিক, সামাজিক, ও দার্শনিক প্রেক্ষাাপটে বিশ্লেষণ করেই আমরা বুঝতে পারি—আজকের দুঃসময়ে কীভাবে তারা আমাদের আলোর পথ দেখাতে পারেন। তারা কেবল কবি নন—তারা আমাদের সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক মুক্তির দিগদর্শী। যেদিন আমরা রবীন্দ্রনাথের হৃদয়ের সঙ্গে নজরুলের হাতের মুষ্টি এবং সুকান্তের চোখের আগুনকে একসূত্রে দেখতে পারব, সেদিনই আমরা আমাদের সাহিত্য-ঐতিহ্যকে সম্পূর্ণভাবে ধারণ করতে পারব।
তথ্যসূত্র
* ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ। চিঠিপত্র (বিভিন্ন খণ্ড), বিশ্বভারতী, কলকাতা।
* ইসলাম, কাজী নজরুল। রচনা সমগ্র, বাংলা একাডেমি, ঢাকা।
* ভট্টাচার্য, সুকান্ত। সুকান্ত সমগ্র, ন্যাশনাল বুক ট্রাস্ট, কলকাতা।
* দাশগুপ্ত, চিত্তরঞ্জন। রবীন্দ্র-নজরুল সম্পর্ক: ইতিহাস ও প্রাসঙ্গিকতা, সাহিত্যম, ১৯৮৫।
* আহমেদ, আনিসুজ্জামান। বাংলা সাহিত্য ও ইতিহাস চেতনা, বাংলা একাডেমি, ২০০২।
* ইমন, হাবীব। বিপ্লবের রণধ্বনি : জীবন-চরিতে সুকান্ত ভট্টাচার্য. পরস্পর (ওয়েবম্যাগ), ২০১৮
* Bose, S.C. (Ed.). Selected Letters of Tagore, Macmillan, 1955.
* Basu, Subho. Revolutionary Passions: Marxism and Literature in Bengal, Oxford University Press, 2015.
* Sengupta, N. (Ed.). Nazrul: Rebel and Prophet, Sahitya Akademi, 1999|
* Ray, Amalendu. Communism in Bengal: From Partition to Naxalbari, Progressive Publishers, 1990.
হাবীব ইমন : লেখক ও রাজনৈতিক বিশ্লেষক