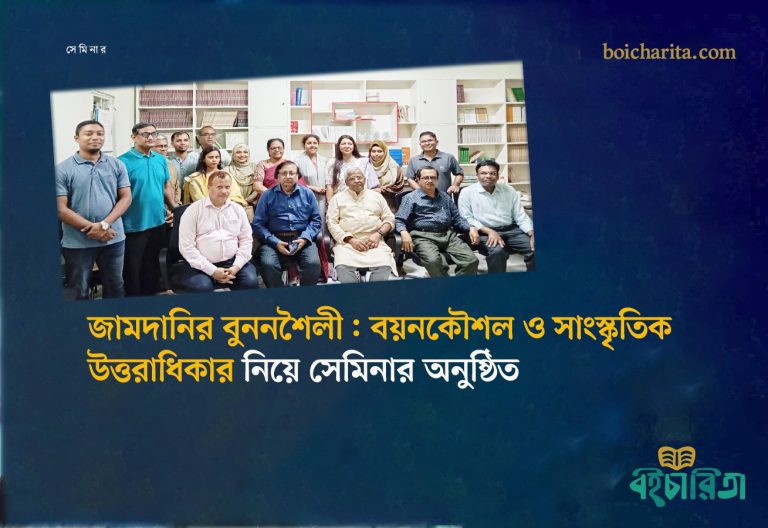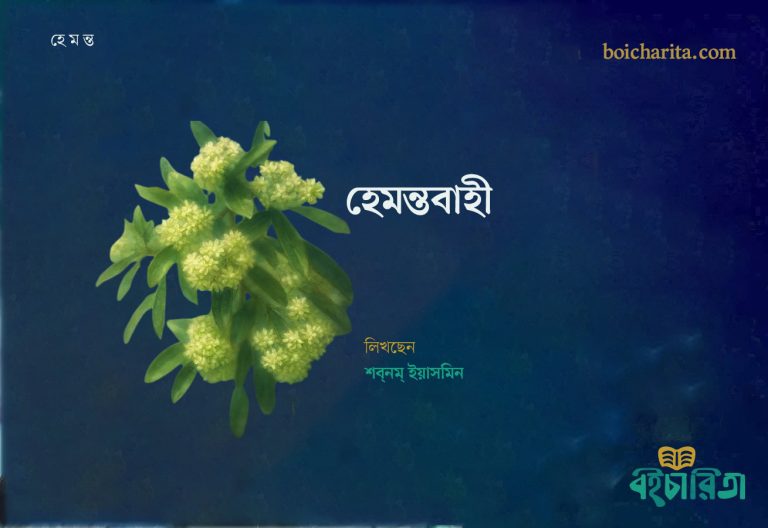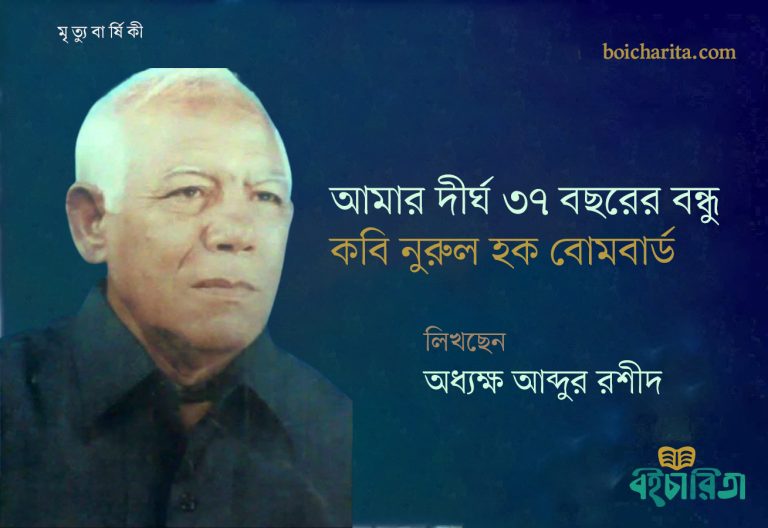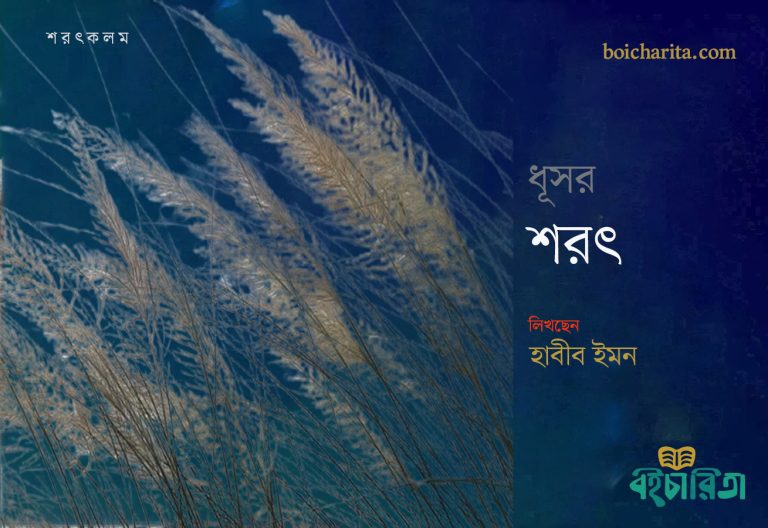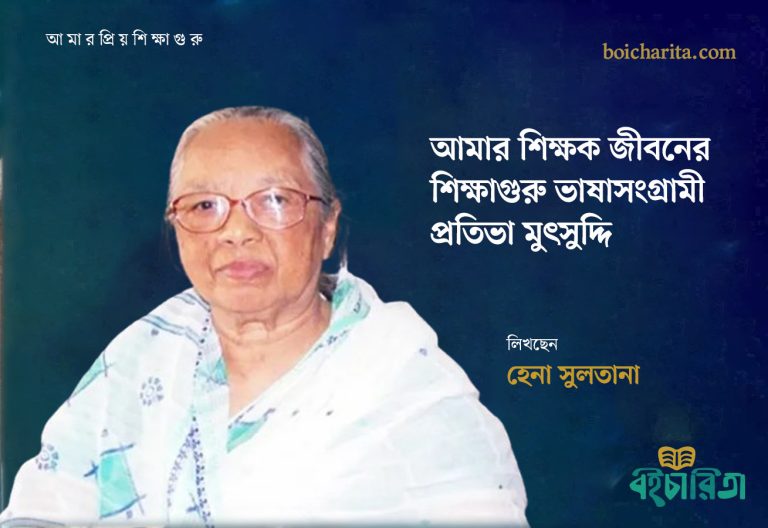সময়ের সাহসী নায়ক প্রফেসর আবদুল জলিল

এক.
প্রয়াত জাতীয় অধ্যাপক কবীর চৌধুরী বলেছিলেন, ‘শিক্ষক হিসেবে তিনি ছিলেন অত্যন্ত প্রজ্ঞাবান। সমাজের গুণীজনদের নিয়ে যতবেশি লেখালেখি হবে ততই আধুনিক ও মননশীল সমাজের পথ প্রসারিত হবে। অধ্যাপক আবদুল জলিলের মতো ভালো মানুষেরা কখনো মরে না।’ আবদুল জলিল প্রয়াত হয়েছিলেন ২০০১ সালের ১৯ সেপ্টেম্বর। তার প্রয়াণের প্রায় এক যুগ পরে শেষ হলো কবীর চৌধুরীর যুগ। তিনি আবদুল জলিলের ইংরেজি বিষয়ে শিক্ষক ছিলেন।
আবদুল জলিল—এক কথায় তিনি স্বনামে ধন্য। বিশেষ করে নোয়াখালী মানুষের কাছে নতুন করে তাঁর পরিচয় দেওয়ার প্রয়োজন নেই সম্ভবত খুব একটা। তিনি একাধারে শিক্ষাবিদ, বাণিজ্য বিষয়ে সুলেখক, অধ্যক্ষ, এক সময়ে খেলোয়াড়, ক্রীড়া সংগঠক। ষাটের দশকের মধ্যভাগে পুঁথিঘর লি. থেকে তাঁর লেখা ব্যাংক-বিধি নামে বইটি প্রকাশিত হয়। মাতৃভাষা বাংলা শিক্ষার মাধ্যম হিসেবে স্বীকৃতি লাভের পর উচ্চমাধ্যমিক শ্রেণির জন্য এ গ্রন্থটি রচনা করেন তিনি। সেই সময়ে বাংলা ভাষায় প্রয়োজনীয় পাঠ্যপুস্তক ছিল না। তিন দশকের বেশি সময় ধরে এ বইটির জনপ্রিয়তা ছিল তুঙ্গে। বলা যায়, বাংলা ভাষার মর্যাদা রক্ষায় এ বইটির ভূমিকা অনন্য। এ ছাড়া ষাটের দশকে নবযাতক নামে একটি সাপ্তাহিক পত্রিকা সম্পাদনা করতেন তিনি।
নোয়াখালী সরকারি কলেজের প্রধান ফটক পেরিয়ে ভেতরে ঢুকলেই যে স্থাপত্যটি প্রথম চোখে ধরা পড়ে, সেটি হলো—‘অধ্যক্ষ আবদুল জলিল অডিটরিয়াম।’ বড়ো করে লেখা নামটি নিঃশব্দে উচ্চারণ করে যায় এক বিস্মৃত কীর্তির ইতিহাস, এক মানুষের জীবনসংগীত। তিনি ছিলেন একজন স্বপ্নদ্রষ্টা শিক্ষাবিদ—যিনি নোয়াখালীর উচ্চশিক্ষার ভার নিজের কাঁধে তুলে নিয়েছিলেন। ছিলেন আলোকবাহক, যিনি অন্ধকারের ভেতরেও বিশ্বাস করতেন আলো একদিন আসবেই। কিন্তু আজ অডিটরিয়ামের সামনে দাঁড়িয়ে কোনো অচেনা পথিকের পক্ষে জানা সম্ভব নয়—নোয়াখালী সরকারি কলেজ আজ যে মহিমায় দাঁড়িয়ে আছে, তার পেছনে এই মানুষের রক্ত, ঘাম আর স্বপ্নের কতটা বিনিয়োগ আছে! যদি অডিটরিয়ামের দেয়ালে তাঁর জীবনের সংক্ষিপ্ত বৃত্তান্ত, প্রতিকৃতি সংরক্ষিত থাকত, তাহলে আগামী প্রজন্মও জানতে পারত—একজন মানুষ কীভাবে স্বপ্নকে স্পর্শযোগ্য করে তোলেন।
দুই.
কেন প্রফেসর আবদুল জলিল কিংবদন্তি, নতুন প্রজন্মের কাছে হয়তো প্রশ্ন জাগতে পারে—কেন এই অডিটরিয়ামের নামকরণ তাঁর নামে? উত্তরটি লুকিয়ে আছে তাঁর সংগ্রামে, তাঁর সাহসিকতায়। একটি অনগ্রসর অঞ্চলের শিক্ষা যখন শিকড় গেড়ে বসতে পারছিল না, যখন দক্ষিণ জনপদের মানুষ উচ্চশিক্ষার স্বপ্ন দেখতে ভয় পেত, তখনই আবদুল জলিল দাঁড়ালেন প্রথম সারিতে। তিনি শুধু কলেজ গড়ে তোলেননি, গড়ে তুলেছিলেন শিক্ষিত সমাজের ভিত।
আবদুল জলিলকে নিয়ে কিছু মিথ আছে, তা হলো, তার মিথ পান খাওয়া বা বড়শি দিয়ে মাছ ধরা। এগুলো নিছক কোনো গল্পে নয়। কিন্তু তাঁর প্রকৃত মিথ লুকিয়ে আছে তাঁর দৃঢ়তায়—নিজের কর্মে অটল প্রতিজ্ঞা হয়ে ওঠার ক্ষমতায়। কেউ কী বলবে, কোনো প্রভাবশালী মহল বিরূপ হবে কিনা, বা কোনো রাজনৈতিক চাপ আসবে কিনা—এসব কোনো কিছুই তাঁর পথ রোধ করতে পারেনি। তিনি ছিলেন ঝড়ের মধ্যে বাতিঘর। একটা সমগ্র দক্ষিণাঞ্চল, যেখানে শিক্ষার আলো ছিল ক্ষীণ প্রদীপের মতো, সেই জনপদের ভেতরে প্রবেশ করে তন্নতন্ন করে খুঁজেছেন সম্ভাবনার বীজ। তিনি জানতেন, উচ্চশিক্ষা কেবল শ্রেণির জন্য নয়, এটি জনগণের অধিকার। আর সেই বিশ্বাস থেকেই তিনি নোয়াখালীর শিক্ষার দ্বার উন্মোচন করেছিলেন। তাঁর উত্তরাধিকাররা আজও যখন কলেজের অডিটরিয়ামের দরজা খোলেন, শিক্ষার্থীদের হাসি-গানে ভরে ওঠে প্রাঙ্গণ, অদৃশ্য এক বাতিঘর হয়ে অধ্যক্ষ আবদুল জলিল সবার পথ দেখান। তিনি ছিলেন কর্মযোগী মানুষ। তাঁর কাছে শিক্ষা কোনো চাকচিক্যের বিষয় ছিল নয়, ছিল এক গভীর দায়বদ্ধতা—মানুষকে মানুষ করে তোলার দায়। তাঁর জ্বালানো শিক্ষার মশাল আজও প্রজন্ম থেকে প্রজন্মে আলো বিলিয়ে চলেছে।
তিন.
ঢাকায় পাকিস্তান ইন্টারন্যাশনাল এয়ারলাইন্সে উচ্চতর পদে যোগ দিয়ে কর্মজীবন শুরু করেন প্রফেসর আবদুল জলিল। এরপর নোয়াখালী কলেজ প্রতিষ্ঠিত হলে বাণিজ্য বিভাগের প্রধান হিসেবে যোগদান করেন। একই কলেজের ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ হিসেবে যোগ দেন ১৯৮৫ সালের ২৭ আগস্ট। ইতিমধ্যে লক্ষ্মীপুর সরকারি কলেজে বদলি হওয়ার পর ১৯৮৯ সালের ২৭ জানুয়ারি নোয়াখালী সরকারি কলেজে পুনঃবদলি হয়ে আসেন। এখানে উল্লেখ্য যে, লক্ষ্মীপুর সরকারি কলেজে বিএসসি ডিগ্রি পাস চালুতে তার বড় অবদান রয়েছে। এর মধ্যে স্বৈরাচার এরশাদ সরকারের একজন শিক্ষামন্ত্রী তার অল্পদিনের কার্যকালের শুরুতে তাকে সন্দ্বীপ আবদুল বাতেন সরকারি কলেজে অধ্যক্ষ হিসেবে বদলি করেন। শিক্ষামন্ত্রী পরিবর্তন হওয়ায় তার এ বদলি আদেশ বাতিল হয়। ১৯৯০-৯১ শিক্ষাবর্ষে নোয়াখালী সরকারি কলেজের পাশাপাশি সেনবাগ সরকারি কলেজে অধ্যক্ষ হিসেবে অতিরিক্ত দায়িত্ব পালন করেন। ১৯৯৭ সালের ২ জুলাই দীর্ঘ ৩৭ বছরের কর্মজীবনের ইতি টেনে প্রিয় কলেজ থেকে অশ্রুসিক্ত ভালোবাসা নিয়ে অবসরগ্রহণ করেন।
অধ্যক্ষ হিসেবে দায়িত্ব নেওয়ার তিনি নোয়াখালী সরকারি কলেজের উন্নয়নের জন্য দিনরাত পরিশ্রম করতে থাকেন। বিভিন্ন দপ্তরে চিঠি চালাচালি করতে থাকেন। তখনকার দিনে টাইপ মেশিন ছিল, কম্পিউটার ছিল না। মাঝে মাঝে নিজেও টাইপ করতেন। বিািভন্ন মন্ত্রণালয়ে তিনি চিঠি পাঠাতেন। চিঠিগুলো লেখা হতো কলেজের উন্নয়নের জন্য। কলেজের আসবাবপত্র লাগবে, কলেজের ফ্যাকাল্টি ভবন লাগবে, কলেজের রাস্তাঘাট নাই, ছাত্রছাত্রীদের অসুবিধা—বেঞ্চ নাই, বসতে পারে না, বাউন্ডারি ওয়াল লাগবে, মাটি বরাদ্দের জন্য, শিক্ষক স্বল্পতা, ইত্যাদি কলেজে যা যা সমস্যা ছিল, তিনি তা সমাধানের জন্য লিখতেন। একেকটি চিঠি পাঁচ-ছয় পৃষ্টা হতো। এরপর তিনি স্বশরীরে ধরনা দিতে থাকেন। কিভাবে কলেজকে এ অঞ্চলের বড় সবচেয়ে বড় বিদ্যাপীঠে পরিণত করা যায়, তার জন্য সব ধরনের উদ্যোগ তিনি নেন। কলেজকে বড় অবয়বে নিয়ে যেতে কলেজ স্থানান্তর করার কাজে তিনি হাত দেন। নিজেদের আধিপত্য হারানোর ভয়ে একটি গোষ্ঠী তখন তার বিরুদ্ধে উঠে-পড়ে লাগে। বিভিন্নভাবে তাকে নাজেহাল করার চেষ্টা করে। নোয়াখালী জেলা শহরের বিভিন্ন দেয়ালে দেয়ালে তাঁর নামে চিকা মারা হয়—‘জলিল তুই কবে যাবি?’ তাঁকে এ কলেজ থেকে সরানোর জন্য বদলি করা হয়। তাঁর দৃঢ়তা তাকে আবার এ কলেজে ফিরিয়ে আনে। তিনি থমকে যাননি। বিভিন্ন চাপ ও হুমকি-ধামকির ভেতরেও নোয়াখালী সরকারি কলেজকে স্থানান্তর করেন। যেদিন কলেজটি বর্তমান বৃহৎ স্থানে স্থানান্তর হয়, সেদিনও তার বাসায় হামলা করা হয়। বহুবার তিনি অপদস্থ হয়েছেন। পুরাতন কলেজ থেকে বাসায় ফেরার সময় রিকশাওয়ালারা তাকে আনতো না। কেননা তাদেরকে রিকশায় না তুলতে বলা হয়েছে।
প্রফেসর আবদুল জলিলের অক্লান্ত পরিশ্রমের ফলে নোয়াখালী সরকারি কলেজে অনার্স ও মাস্টার্স কোর্স চালু হয়, যা ছিল বৃহত্তর নোয়াখালী অঞ্চলের প্রাণের দাবি। ১৯৯১-১৯৯২ শিক্ষাবর্ষে বাংলা, রাষ্ট্রবিজ্ঞান ও হিসাববিজ্ঞানে অনার্স কোর্সে ছাত্র-ছাত্রী ভর্তি করাই। যদিও তখন তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রয়োজনীয় অনুমোদন পাননি। এটা ছিল একধরনের ঝুঁকি ও অনিশ্চয়তা। কিন্তু তিনি বিশ্বাস করতেন—‘অনেষ্টি থাকলে ঠেলি খেললে ফ্উাল নেই’। অনার্স পরীক্ষা চলে আসছে। কিন্তু অনুমোদন পাওয়া যায়নি। পরবর্তীতে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ তাকে তথা এ কলেজকে অনুমোদন দিতে বাধ্য হয়। সেসময়ে অনেকেই তাবে তিরষ্কার করেছেন। বলেছেন, ‘এখানে কীসের অনার্স কোর্স চালু হবে?’ তাকে অনেকে বিদ্রুপ করেছেন। অনেকভাবে তাকে নাজেহাল করার চেষ্টা করেছে। তিনি ব্যক্তিগত অনেককে ধরে এনে এ কলেজে ভর্তি করেছেন। যারা কিনা ঢাকা, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়মুখী হওয়ার জন্য প্রস্তুত ছিল এবং ওখানে ভর্তি হওয়ার যোগ্যতা রাখে। অনেক সময় তিনি নিজে অনার্সের ক্লাস করাতেন। প্রচন্ড ব্যস্ত একজন অধ্যক্ষ ক্লাস করাবেন, এটা ভাবতে পারতেন না তার ছাত্ররা। এখানে আরেকটি কথা উল্লেখ করতে হয়, হিসাববিজ্ঞানে অনার্স খোলার সময় ওই বিভাগের শিক্ষক হিসেবে অন্তুর্ভূক্ত করেন, যাতে অনার্স চালু হতে সমস্যা না হয়। এখানে আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ তথ্য যোগ করা দরকার, ১৯৮৭ সালে পুরানো নথিপত্র পোড়ানোর হিড়িকে অনেক মূল্যবান কাগজপত্র পুৃড়িয়ে ফেলা হয়েছে, তখন তিনি এ কলেজে কর্মরত ছিলেন না, যার ফলে পরে অধ্যক্ষ হিসেবে দায়িত্বগ্রহণের পর নতুন করে কাগজপত্র তৈরি করতে হয়েছে।
১৯৯১-৯২ শিক্ষাবর্ষে আরও ছয়টি বিষয়ে অনার্স কোর্স প্রবর্তনের প্রস্তাব পেশ করেন। এ ছাড়া, ১৯৯৪ সালে পাঁচটি বিষয়ে মাস্টার্স কোর্স প্রবর্তনের অনুমতি লাভ করেন। ১৯৯৪-৯৫ শিক্ষাবর্ষে হিসাববিজ্ঞান, বাংলা, রাষ্ট্রবিজ্ঞানে মাস্টার্স প্রথম পর্বে ছাত্র-ছাত্রী ভর্তি করানো হয়। ১৯৯৬-৯৭ শিক্ষাবর্ষে ব্যবস্থাপনা ও অর্থনীতিতে মাস্টার্স কোর্স চালু হয়। এভাবে কালক্রমে গণিত, সমাজবিজ্ঞান, ইংরেজি, পদার্থবিদ্যা, রসায়ন, উদ্ভিদবিদ্যা, প্রাণীবিজ্ঞান, অর্থনীতিসহ মোট ১২টি বিষয়ে অসার্স কোর্স চালু করার প্রয়োজনীয় অনুমোদন এ শিক্ষাবিদের বর্ণাঢ্য ও কর্মময় প্রচেষ্টা ও সাধনার ফসল। কেবলমাত্র অনার্স ও মাস্টার্স চালু করে তিনি ক্ষান্ত হননি, প্রত্যেকটি বিষয়ে তিনি প্রয়োজনীয় পদসৃষ্টি করেন। পদ সৃষ্টির মতো একটি জটিল দুরুহ বিষয় অত্যন্ত পারদর্শিতার সঙ্গে তিনি সফল হলেন, যা তখনকার শীর্ষস্থানীয় কলেজ সক্ষম হয়নি।
নোয়াখালী সরকারি কলেজের সাবেক অধ্যক্ষ প্রফেসর মোস্তাফিজুর রহমান ‘স্মরণের আবরণে জলিল ভাই’ শিরোনামে একটি লেখায় লিখেন, ‘একনিষ্টতার সাথে উদ্যমের সাথে অধ্যক্ষের দায়িত্ব পালন করেছেন। শুধু অফিসিয়াল দায়িত্ব পালন করেননি, কা-ারি হিসেবে যা কিছু করার দরকার তাই করেছেন। পুরাতন ভবনে থাকার সময়, পুরাতন ভবন থেকে নতুন অবস্থানে স্থানান্তরের সময়, নতুন ভবনের (ডিগ্রি পাস, অনার্স, মাস্টার্স ক্যাম্পাস) ভূমি অধিগ্রহণের সময়, ভৌত অবকাঠামোর সময়, অ্যাকাডেমিক কাঠামো বির্নিমাণকালে ক্লান্তিহীন পরিশ্রম করেছেন।’
১৯৯৪ সালে সরকার থেকে সিদ্ধান্ত হয়, অনার্স-মাস্টার্স আছে, এমন সরকারি কলেজে এইচএসসি থাকবে না। সে সিদ্ধান্তে অনেক কলেজে এইচএসসি তুলে নেওয়া হয়। নোয়াখালী সরকারি কলেজেও তুলে নেওয়ার চিঠি আসে। প্রফেসর আবদুল জলিল সেই চিঠির তোয়াক্কা না করে সেই বছরই একাদশ শ্রেণিতে ছাত্র-ছাত্রী ভর্তি করান। ১৯৯৬ সালে বাধ্য হয়েই উচ্চ মাধ্যমিক শ্রেণি পুরাতন ক্যাম্পাসে স্থানান্তর করতে হয়। ছাত্রদের বহুমুখী ও কর্মমুখী বিষয় পাঠের সুবিধা প্রদানের লক্ষ্যে পরিসংখ্যান ও কম্পিউটার বিজ্ঞান কোর্স প্রবর্তন করেন। তিনি চেয়েছিলেন পুরাতন ক্যাম্পাসে একটি বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি কলেজ—যেটা নোয়াখালী সরকারি কলেজের একটি সংলগ্ন কলেজ হিসেবে থাকবে। কেবলমাত্র নোয়াখালী সরকারি কলেজ উন্নয়ন নয়, তিনি এ অঞ্চলে বিভিন্ন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান সরকারিকরণে তাঁর নিরলস ভূমিকা রয়েছে।
চার.
তিনি ছাত্র-ছাত্রীদের খুব ভালোবাসতেন। দলমত নির্বিশেষে নিজের সন্তানের চাইতে বেশি স্নেহ করতেন। তার কলেজের কোনো ছাত্রনেতা অ্যারেস্ট হলে তিনি সরাসরি ফোন করে ‘আমার কলেজের ছাত্র’ বলে ছাড়িয়ে আনতেন। ব্যক্তিগতভাবে জামিন করে ছাড়িয়ে আনতেন। কিন্তু অন্যায়কে প্রশ্চয় দিতেন না। কোনো রক্তচক্ষুকে ভয় পেতেন না। একবার কলেজের এক ছাত্রের নামে শিক্ষা বোর্ড থেকে একটি ভুয়া সার্টিফিকেট ইস্যু হয়। তার বিতরণের সময়ে আবদুল জলিলের নজর এড়ায় না। ইস্যুকৃত সনদে অফিসারের সই জাল হয়েছে বলে তিনি স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হন, এবং পুলিশের কাছে সোর্পদ করেন ওই ছাত্রকে।
তিনি ছোট ছোট কাগজকে ব্যবহার করতেন। সেগুলোতে চিরকটু লিখতেন। একটা কাগজকে কেটে তিন ইঞ্চি বাই তিন ইঞ্চি কাগজ করে ছোট ছোট নোট লিখতেন। অনেকেই এ নোটগুলোকে কৃচ্ছতাসাধন করছেন বলে উপহাস করতেন। তিনি অনেক শিক্ষককে চিরকুট লিখতেন, লিখে পাঠাতেন। চিরকুটটা ছিল বিশেষ ফরম্যাটে লেখা, প্রথমে বকুনি, তারপর একটা যুক্তি, সর্বশেষ নির্দেশ। হয়তো ভিন্নতা ছিল, কিন্তু এই চিরকুটগুলোই ছিল প্রফেসর আবদুল জলিলের ব্যাপক প্রাণবন্ত যোগাযোগের মূল ভিত্তি। অনেকগুলো অনুকরণীয় বৈশিষ্ট্যের মধ্যে একটি ব্যতিক্রমী বৈশিষ্ট্য হচ্ছে তার চিরকুট লেখা।
প্রফেসর আবদুল জলিলের এই অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ নোয়াখালী সরকারি কলেজের অডিটরিয়ামের নামকরণ হয়েছে অধ্যক্ষ আবদুল জলিল অডিটরিয়াম। ২০০৪ সালের ১৩ অক্টোবর অডিটরিয়াম উদ্বোধনকালে তৎকালীন আইন-বিচার ও সংসদবিষয়ক মন্ত্রী ব্যারিস্টার মওদুদ আহমেদ বলেন, ‘বৃহত্তর নোয়াখালীর স্বনামধন্য, আমার প্রিয় শিক্ষাবিদ প্রফেসর আবদুল জলিলের নামে অডিটরিয়াম উদ্বোধন করতে পেরে আমি গর্বিত।’
আবদুল জলিল কেবলমাত্র একজন দক্ষ শিক্ষক ছিলেন কিংবা প্রশাসক হিসেবে স্বীকৃতি নন— বাণিজ্য বিষয়ে একজন সুলেখক হিসেবে রয়েছে তাঁর যথেষ্ট সুখ্যাতি। তিনি ছয়টি গ্রন্থ রচনা করেন। তাঁর রচিত বাংলাদেশের বাণিজ্যিক ও শিল্প আইন, ব্যাংক-বিধি, অ্যা টেক্সট বুক অব ব্যাংকিং, অ্যাডভান্সড অ্যকাউন্টান্সি মেড ইজি উল্লেখযোগ্য। এছাড়া, তিনি একজন কৃতি খেলোয়াড় ছিলেন। ১৯৫৯-৬০ ও ৬০-৬১ শিক্ষাবর্ষে তিনি আন্তঃবিভাগ ও আন্তঃহল ক্রীড়া সমিতির সাধারণ সম্পাদক ছিলেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে কৃতিত্বপূর্ণ অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ বিশেষ সনদ (ব্লু) লাভ করেন।
পাঁচ.
কীর্তিমান শিক্ষাবিদ প্রফেসর জলিলের স্বপ্ন ছিল নোয়াখালী সরকারি কলেজ একদিন বিশ্ববিদ্যালয়ে রূপান্তরিত হবে। বর্তমান স্থানে জায়গার সংকট রয়েছে। কলেজের জন্য আরও কিছু জায়গা বরাদ্দের জন্য প্রস্তাব করেছিলেন। ব্যাংকের শাখা চালু, আধুনিক ক্যাফেটেরিয়াসহ আরও অনেক কিছু করার ইচ্ছে ছিল তার। তিনি পূর্ণাঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয় গড়ার ভিত্তি তৈরি করে গেছেন, পথ প্রস্তুত করে গেছেন। হয়তো একদিন তার সেই স্বপ্ন পূর্ণ হবে।
প্রফেসর আবদুল জলিল কেবল একজন শিক্ষাবিদ নন—তিনি সময়ের সাহসী নায়ক। ঝড়-ঝঞ্ঝার ভেতর দাঁড়িয়ে তিনি জ্বালিয়েছিলেন শিক্ষার প্রদীপ। যেখানে অন্ধকার ছিল, সেখানে তৈরি করেছিলেন আলো। আজ তিনি নেই, কিন্তু তাঁর হাতের গড়া প্রতিষ্ঠান তাঁর জীবনের সাক্ষ্য হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। তিনি আছেন—প্রত্যেক শ্রেণিকক্ষের কোলাহলে, প্রত্যেক স্বপ্নের আলোয়, প্রত্যেক শিক্ষার্থীর চোখের ঝিলিকে। প্রফেসর আবদুল জলিল—আমাদের ও অনাগত প্রজন্মের জন্য চিরদিনের বাতিঘর।
তথ্যসূত্র :
* স্মৃতি থেকে নোয়াখালী সরকারি কলেজ : প্রতিষ্ঠা, স্থানান্তর ও উন্নয়ন, প্রফেসর আবদুল জলিল (প্রকাশিতব্য)
* সাক্ষাৎকার, মার্চ ১৯৯৭, লক্ষ্মীপুর বার্তা
* সাক্ষাৎকার, মার্চ ১৯৯৭, বিশ^বিদ্যালয় ক্যাম্পাস
* বৃহত্তর নোয়াখালীর বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব : ২৪৯-অধ্যক্ষ আবদুল জলিল, ড. খালেদ মাসুকে রসুল, দৈনিক জাতীয় নিশান, ১৬ জানুয়ারি ১৯৯৪
* সাপ্তাহিক সমকাল বার্তা. ৭ মে ২৯৯২
* অবিকল্প জলিল স্যার, কাজী এবিএম শাহজাহান শাহীন, অধ্যক্ষ আবদুল জলিল : স্মৃতিজল সুধায় আজন্ম, সম্পাদক আবুল বাশার ও হাবীব ইমন
* নোয়াখালী সরকারি কলেজ ও আবদুল জলিল একটি অপ্রকাশিত অধ্যায়, মুহাম্মদ সামছুল ফারুক, অধ্যক্ষ আবদুল জলিল : স্মৃতিজল সুধায় আজন্ম, সম্পাদক আবুল বাশার ও হাবীব ইমন
হাবীব ইমন : কলামলেখক, সাংবাদিক, রাজনৈতিক বিশ্লেষক।