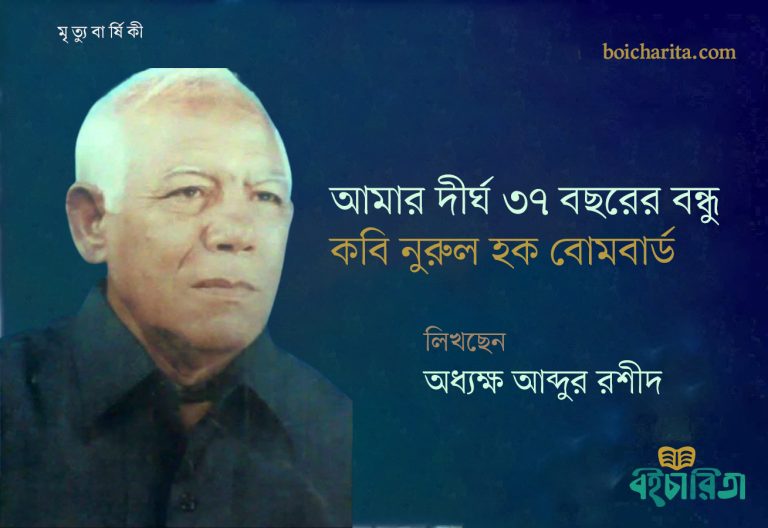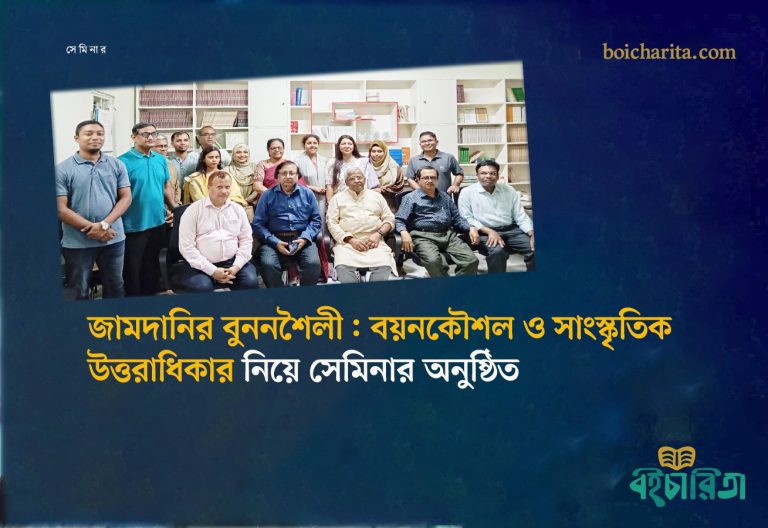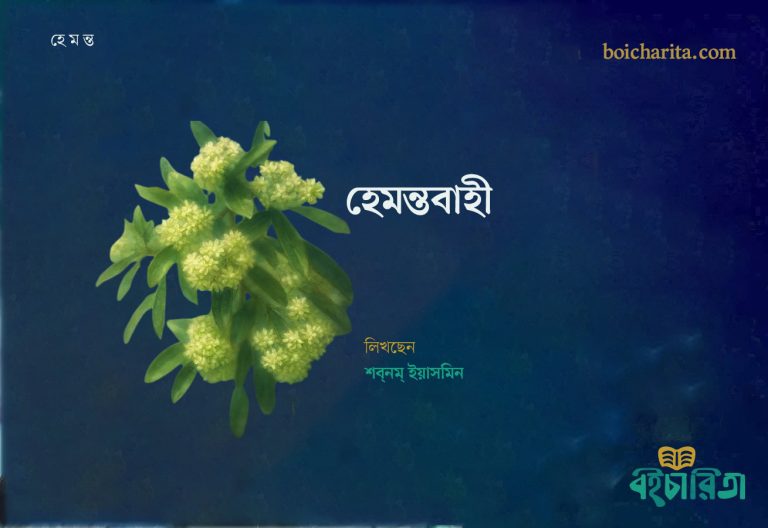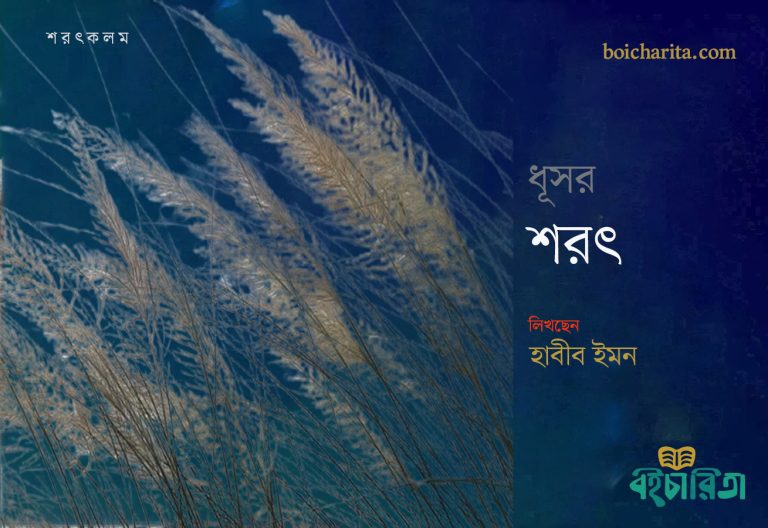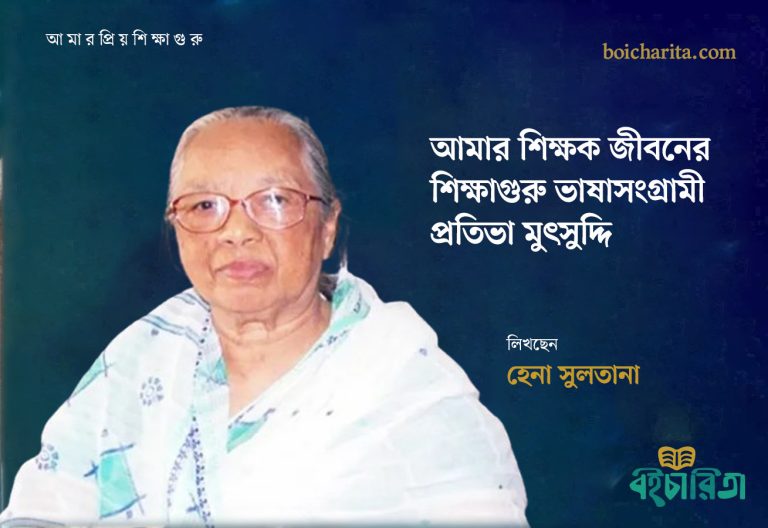কেমন হওয়া উচিত ছাত্ররাজনীতি

কয়েক বছরে আমরা দেখেছি, ছাত্ররাজনীতি মানে প্রতিপক্ষের ওপর হামলা, নিজেদের মধ্যে মারামারিতে জড়ানো, এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছে চাঁদাবাজি আর ছিনতাই। এ ছাড়া বিভিন্ন ভর্তি পরীক্ষা ও নিয়োগ পরীক্ষার প্রশ্নপত্র ফাঁসের সঙ্গে ছাত্রনেতাদের নাম আসার খবরও দেখেছি। আমাদের সামনে দুর্বৃত্তপনার যেসব নতুন নতুন নজির হাজির হয়েছে, তা হতাশার, একইসঙ্গে গ্লানিরও। দেশে এমন কোনো বিশ্ববিদ্যালয়-কলেজ খুঁজে পাওয়া যাবে কি না সন্দেহ, যেখানে ছাত্রলীগের ক্ষমতার দাপট এবং নানান অপরাধমূলক কাজের চিহ্ন নেই।
চারপাশে দখলের রাজনীতির বদৌলতে ছাত্ররাজনীতির হল দখল মূলত অনৈতিকতা ও হিংসা-ক্রোধের পরিসর হয়ে উঠেছে, ফলে যেখানে প্রত্যক্ষভাবে দখলের প্রশ্ন নেই, সেখানেও হিংসা আছে। রাষ্ট্রযন্ত্র ছাত্ররাজনীতির এ শৃঙ্খলাহীনতাকে ‘স্বাভাবিক’-এর স্বীকৃতি দেওয়ায় এ আচরণগুলো বস্তুত অনিবার্য হয়ে উঠেছে।
এমন পরিস্থিতিতে প্রশ্ন তৈরি হয়েছে, ছাত্ররাজনীতির কি কোনো প্রয়োজন আছে? আমি মনে করি, ছাত্ররাজনীতি নয়, আদর্শিক ও নীতিনিষ্ঠ অবস্থান না থাকায় দুর্বৃত্তপনার সুযোগ ঘটেছে। ছাত্রলীগ-ছাত্রদল-ছাত্রশিবির যে যখন ক্ষমতায় ছিল, তখন তারা একক-নিরঙ্কুশ ভয়ংকর রাজনীতি করেছে। বর্তমান প্রজন্ম এটা জানে না, তারা দেখেননি, একসময় ছাত্রদলের জুলুমের রাজনীতি, আর শিবিরের রগকাটা রাজনীতি কত ভয়ংকর ছিল। সেগুলো হয়তো দূরের গল্প।
মতাদর্শই হলো ছাত্র-আন্দোলন ও ছাত্ররাজনীতির জিয়নকাঠি। ঘটনা হলো, যখনই মতাদর্শ নতুন স্বপ্ন দেখিয়েছে, ছাত্রসমাজ উদ্বেল হয়েছে। স্বাধীনতার স্বপ্ন—গণতান্ত্রিক কাঠামো রক্ষার স্বপ্ন তাদের উদ্বুদ্ধ করেছে। আজকের ছাত্র আন্দোলনের দুরবস্থার মূল কারণ লুকায়িত রয়েছে এখানেই—তাদের সামনে নতুন মতাদর্শ বা স্বপ্ন নেই। সাম্প্রতিক ছাত্র-আন্দোলনের পুনরুত্থান দাবি করছে মতাদর্শের পুনর্নির্মাণ। অনেকেই ঐতিহ্যের কথা বলেন। ঐতিহ্যের অর্থ কখনো পুরোনো চিন্তার দাসত্ব নয়। পুরোনো ঐতিহ্য রক্ষা করে শর্ত ভেঙে বারবার নতুন ঐতিহ্য গড়ে ওঠে। সমসাময়িক ছাত্র-আন্দোলনই তার সাক্ষী।
দুই
যুক্তরাষ্ট্রের সাবেক প্রেসিডেন্ট আব্রাহাম লিংকন বলেছিলেন, ‘ছাত্রজীবন থেকে যারা রাজনীতি করে তারাই প্রকৃত রাজনীতিবিদ হয়ে ওঠে।’ এখানে বেশ কয়েকটি বিষয় প্রাসঙ্গিক। প্রথমটি হলো রাজনীতি, দ্বিতীয়টি ছাত্ররাজনীতি, তৃতীয়টি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে রাজনৈতিক আচরণটা কেমন হওয়া উচিত।
এটা সত্য বায়ান্ন ও এর পূর্বাপর ভাষা আন্দোলন, বাষট্টির ছাত্র আন্দোলন, উনসত্তরের গণ-অভ্যুত্থান কিংবা নব্বইয়ের স্বৈরাচারবিরোধী আন্দোলনে ছাত্ররাজনীতির একটা গুরুতত্বপূর্ণ ভূমিকা আছে। বোধ হয় তারুণ্য ও সংগ্রামকে ঘিরে হেলাল হাফিজ তাঁর সেই বিখ্যাত কবিতা ‘এখন যৌবন যার মিছিলে যাবার তার শ্রেষ্ঠ সময়, এখন যৌবন যার যুদ্ধে যাবার তার শ্রেষ্ঠ সময়, মিছিলের সব হাত/কণ্ঠ/পা এক নয়’ লিখেছিলেন।
যে রাজনীতি শিক্ষার্থীদের পড়তে দেয় না, ঘুমাতে দেয় না, শান্তিতে থাকতে দেয় না, স্বাধীনভাবে চলাফেরা, মতপ্রকাশ করতে দেয় না, চাঁদাবাজি, হল দখল করে, হলে হলে টর্চার সেল তৈরি করে, ক্ষমতার লাঠিয়াল হিসেবে কাজ করা সেটা আর যাই হোক ছাত্ররাজনীতি নয়। কাজেই দেশে ছাত্ররাজনীতি নেই। যেটা আছে, সেটা হলো নষ্ট হওয়া, পচে যাওয়া জাতীয় রাজনীতির চুইয়ে পড়া একটা চর্চা। ছাত্ররাজনীতির এ পচে যাওয়া অবস্থা যদি চলতে থাকে, দেশের ভবিষ্যৎ রাজনীতি আরও দুর্গন্ধ ছড়াবে।
তিন
ছাত্ররাজনীতি বলতে কী বোঝায় কিংবা এর আওতা কতটুকু, তার ব্যাখ্যা দরকার। ছাত্ররাজনীতি মানে কি ক্ষমতাসীন দলের লেজুড়বৃত্তি করা? বড় নেতার আশ্রয়-প্রশ্রয়ে থেকে চাঁদাবাজি-টেন্ডারবাজি করা? বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন নিয়োগে বলপ্রয়োগ করা কিংবা এই সূত্রে গোপনে অর্থের লেনদেন করা? সাধারণ ছাত্রদের ওপর নিপীড়নমূলক কর্মকাণ্ড চালানো এবং আবাসিক হলগুলোয় নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করা? বয়স পার হয়ে গেলেও যেকোনো উপায়ে হলে থেকে রাজনৈতিক কর্মসূচিতে খবরদারি করা? নিশ্চয়ই এগুলো ছাত্ররাজনীতির চিত্র হতে পারে না।
তাহলে ছাত্ররাজনীতি কী? ছাত্ররাজনীতি মানে নিজেদের কর্তব্য নির্ধারণ করতে পারা এবং কর্তব্য পালনে দায়িত্বশীল থাকা, সাধারণ ছাত্রদের অধিকার আদায়ের ব্যাপারে সরব ও সচেষ্ট থাকা, প্রাতিষ্ঠানিক ও সামাজিক উন্নয়নে কাজ করা, জাতীয় ও আন্তর্জাতিক বিভিন্ন ইস্যুতে সচেতন থাকা ও মতপ্রকাশ করা, বিভিন্ন সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডের পাশাপাশি মুক্তচিন্তা ও বাক স্বাধীনতার জন্য কাজ করা।
চার
ছাত্ররাজনীতিসহ দলীয় রাজনীতিকে দূষিত করার ফলে এখন দেশে একটা রাজনীতিবিমুখ প্রজন্ম বেড়ে উঠছে। এরা রাজনীতি পছন্দ করে না, রাজনীতিকে ভয় পায়, এড়িয়ে চলে। তাই তো ওদের ভেতর থেকে আওয়াজ এসেছে, ছাত্ররাজনীতি নিষিদ্ধ করতে হবে। তাহলে কি এই দাঁড়াচ্ছে যে ব্যর্থ হয়ে যাবে গণতান্ত্রিক সব আন্দোলন, মুক্তিযুদ্ধ, স্বৈরাচারবিরোধী আন্দোলন ও একটি স্বাধীন দেশের রাজনৈতিক বাঁক বদলে ছাত্ররাজনীতির অবদান? ষাটের দশকের আন্দোলন যেমন আগের ছাত্র আন্দোলনের যুগপৎ কনটিউনিয়েশন অ্যান্ড নেগেশন, একবিংশ শতাব্দীর ছাত্র-আন্দোলনও হবে ষাটের দশক বা নব্বই দশকের কনটিউনিয়েশন অ্যান্ড নেগেশন শুধু পুনরাবৃত্তি নয়, শুধু নাকচ নয়। হয়তো একবিংশ শতাব্দীর বাস্তবতায় এভাবেই ষাটের দশকের ছাত্র-আন্দোলনের নবায়ন ঘটবে।
নিশ্চয় এটা জাতীয় রাজনীতির একধরনের পাইপলাইন, যার এক প্রান্ত দিয়ে ছাত্ররাজনীতির নামে ঢুকে, আরেক প্রান্ত দিয়ে নেতা হয়ে বের হওয়া যায়। তবে কাঁচামাল যদি নিম্নমানের হয়, তাহলে এ পাইপলাইন দিয়ে উৎপাদনও নিম্নমানে হওয়ার কথা। আর এ নিম্নমানের নেতৃত্বের ওপর ভরসা করে আমরা যদি উন্নত বাংলাদেশের স্বপ্ন দেখি, তা হবে অরণ্য রোদন। এ কথা সত্য, বর্তমান রাজনীতি এতটাই কদর্মাক্ত, কেউই এই কাদা গায়ে মাখতে চায় না। কিন্তু এ কথা ভুলে গেলেও চলবে না, জঞ্জাল পরিষ্কারে নিজের গায়েও কিছু ময়লা লাগবে ঠিকই, কিন্তু কোমরে গামছা বেঁধে শক্ত চোয়ালে পণ করে মাঠে নামলে এ ময়লা ঠিকই পরিষ্কার হবেই। শিক্ষার্থীদের স্বার্থেই রাজনীতিতে সংস্কার দরকার। শিক্ষার পরিবেশ এবং সাংস্কৃতিক চর্চাটা সুস্থ করতে পারি, তাহলে নতুন ধারা তৈরি হবে। তার জন্য আমাদের শিক্ষাব্যবস্থাকে বিজ্ঞানভিত্তিক-সংস্কৃতিমনস্ক করে ঢেলে সাজাতে হবে।
ছাত্ররাজনীতি থেকে জাতীয় রাজনীতির লেজুড়বৃত্তি সম্পূর্ণভাবে বর্জন করা প্রয়োজন। ছাত্রসংগঠনগুলোকে শুধু খাতায়-কলমে রাজনৈতিক দল হতে বিচ্ছিন্ন করলেই হবে না। রাজনৈতিক দলগুলোর সঙ্গে ছাত্ররাজনীতির সম্পূর্ণ বিচ্ছেদ না হলে এ পরিবর্তন অর্থহীন হবে। রাজনৈতিক দলের লেজুড়বৃত্তি এবং একদলীয় আধিপত্যের অবসান ঘটলে স্বাভাবিকভাবেই ছাত্রসংগঠন এ রকম বেহাড়া দুর্বৃত্তপনার আখড়ায় পরিণত হবে না। রাজনৈতিক রংহীন ছাত্ররাজনীতি কেমন হতে পারে, তার উদাহরণও সাম্প্রতিক সময়ে ছাত্র-আন্দোলন। শিক্ষার্থীবান্ধব ছাত্ররাজনীতি চর্চা বাড়াতে হবে। সেই রাজনীতিতে একটা ‘গণচরিত্র’ থাকতে হবে। ছাত্ররাজনীতিতে কয়েকটা বিষয় মোটাদাগে থাকা উচিত, সেগুলো হলো পাঠচক্র, বইপড়া, রাজনৈতিক তত্ত্ব ও সমসাময়িক বিষয়ে প্রশিক্ষণ, দেয়াললিখন কর্মশালা, সাহিত্য সংস্কৃতি চর্চা। আমরা যারা ছাত্ররাজনীতি করেছি, নিজেরা জিঘাংসু মন নিয়ে আলোচনা করতাম, সেগুলো বোঝার চেষ্টা করতাম, কি ঘটছে, কেন হচ্ছে। তর্ক হতো, বিতর্ক হতো। তার ভেতর দিয়েই আমাদের রাজনীতি চর্চায় গতিপ্রকৃতি নির্ধারণ করতে পেরেছি।
প্রতিটি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে ছাত্রসংসদকে কার্যকর করতে হবে। যেখানে শিক্ষার্থীরা তাদের বিষয়ে মন খুলে, প্রাণ খুলে কথা বলবেন। যে ধরনের ছাত্ররাজনীতির মধ্য দিয়ে শিক্ষার্থীদের মনস্তাত্ত্বিক বিকাশ ঘটবে এবং নেতৃত্ব তৈরির পাইপলাইন হবে, সে ধরনের রাজনীতি প্রয়োজন। ছাত্রসংসদ কার্যকর হলে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক আবহাওয়ারও বদল হবে। সবচেয়ে বড় কথা, সাধারণ ছাত্রদের অধিকার ও সুযোগ প্রতিষ্ঠিত না হলে শিক্ষার মহৎ লক্ষ্যও অপূর্ণ রয়ে যাবে। শুধু বলতে চাই ছাত্ররা যদি সুস্থ রাজনীতির চর্চা করতে না পারে, তাহলে আসলেই সবকিছু নষ্ট মানুষদের দখলে চলে যাবে। প্রতিহিংসার বিকল্প হিসেবে ইতিবাচক, গঠনমূলক রাজনীতির ধারায় ছাত্ররাজনীতিতে আনতে হবে সংস্কার।